বিবিসি আর্থ-এ প্রকাশিত মাইকেল মার্শাল এর লেখা দ্য সিক্রেট অফ হাউ লাইফ অন আর্থ বিগ্যান অবলম্বনে এই লেখা। থাকছে কয়েক পর্বে।
পৃথিবীর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এখন প্রাণের উল্লাস। তবে সৃষ্টির গোড়াতে ছিল পৃথিবী ছিল নিষ্প্রাণ। তাহলে কীভাবে এই গ্রহে প্রাণের যাত্রা শুরু হলো? এর চেয়ে বড় কোনো প্রশ্ন আর হতে পারে না।
গত প্রায় একশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল তা খুঁজতে গিয়ে নিরন্তর গবেষণা করেছেন এবং সেই গবেষণা এখনও চলমান। এমনকি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে সৃষ্টির শুরুতে পৃথিবীর যেমন পরিবেশ ছিল কৃত্রিমভাবে প্রায় তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রাণহীন বস্তু থেকে প্রাণ সৃষ্টির চেষ্টাও করেছেন।
তবে এখনও বিজ্ঞানীরা সে কাজে সফল হতে পারেননি। এরপরেও বর্তমানে যেসব বিজ্ঞানী প্রাণের উৎপত্তির রহস্য সমাধানে গবেষণা করছেন, তারা অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী যে তারা সঠিক পথেই রয়েছেন। বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই তাদের এই আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে।
প্রাণের উৎপত্তির প্রকৃত উৎস আবিষ্কারে বিজ্ঞানীদের অন্বেষণের রয়েছে এক দীর্ঘ গল্প। প্রাণের সৃষ্টি রহস্য উন্মোচন প্রচেষ্টার সেই গল্প মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ, সংগ্রাম এবং অসাধারণ সৃষ্টিশীলতায় পরিপূর্ণ। যার মধ্য দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের বড় বড় কয়েকটি আবিষ্কারও সম্ভব হয়েছে। বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাণের সৃষ্টি রহস্য সমাধানে মানব-মানবীকে যেতে হয়েছে পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় এবং সহ্য করতে হয়েছে অবর্ণনীয় কষ্ট। অনেক বিজ্ঞানীকে শয়তান আখ্যা দিয়ে নিপীড়ন করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানীকে কাজ করতে হয়েছে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী সরকারের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে। আসুন জেনে নেয়া যাক সেই রোমাঞ্চকর গল্প।
প্রাণ অনেক পুরনো। ডায়নোসর সম্ভবত পৃথিবীর বিলুপ্ত প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে তারা দোর্দণ্ড প্রতাপে টিকে ছিল। কিন্তু প্রাণের উৎপত্তি খুঁজতে আরও সুদূর অতীতে যেতে হবে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের অনুমান, আজ থেকে প্রায় ১৪০০ কোটি বছর আগে যাত্রা শুরু হয়েছিল আমাদের এই মহাবিশ্বের। তার ৯৫০ কোটি বছর পরে আজ থেকে প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয় আমাদের পৃথিবীর। আর এই পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল সম্ভবত আরও ৫০ থেকে ১০০ কোটি বছর পরে, সম্ভবত আজ থেকে ৩৫০-৪০০ কোটি বছর আগে।
আমাদের চেনাজানা সবচেয়ে পুরনো জীবাশ্মের বয়স প্রায় ৩৫০ কোটি বছর, যা কিনা সবচেয়ে পুরনো ডায়নোসরের থেকেও ১৪ গুণ বেশি পুরোনো। তবে ভবিষ্যতে এরচেয়ে প্রাচীন জীবাশ্মের সন্ধানও হয়ত মিলতে পারে।
উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ২০১৬ সালের আগস্টে গবেষকরা ৩৭০ কোটি বছর আগেকার এক আণুবীক্ষণিক অনুজীবের ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন।
আমরা ধরে নেই প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল পৃথিবীতেই; যা যুক্তিযুক্তও মনে হয়। কেননা এখনও আমরা পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও প্রাণের অস্তিত্ত্ব খুঁজে পাইনি। পৃথিবী সৃষ্টির পর এর বয়সের প্রথম ১০০ কোটি বছরের মধ্যেই হয়ত এতে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল।
৪৫০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি আমাদের পৃথিবীর। আর প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনটির বয়স প্রায় ৩৭০ কোটি বছর। আমরা যদি প্রাণের বিকাশ মুহূর্তের কাছাকাছি সময়েও যেতে পারি, তাহলেও সৃষ্টিলগ্নে কেমন ছিল প্রাণের বৈশিষ্ট্য, তার ধারণাও হয়ত পাব।
১৯ শতক থেকে জীববিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবেই জানেন সব ধরনের জীবিত স্বত্ত্বাই জীবন্ত ‘প্রাণকোষ’ দিয়ে গঠিত; যা মূলত বিভিন্ন রকম এবং আকারে অতি ক্ষুদ্র জীবিত অণুর সমষ্টি। ১৭ শতকে আধুনিক মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর প্রথম প্রাণকোষ আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু কোষ থেকেই প্রাণের উৎপত্তি সেটা বুঝতে আরও প্রায় এক শতাব্দী সময় লেগে যায়।
এখন প্রথম প্রাণের উৎপত্তি বা সৃষ্টির বিষয়টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নিরিখে প্রমাণ করতে গেলে অর্থাৎ শূন্য থেকে একটা কোষ সৃষ্টি করতে হলে সেই ৩৫০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর পরিবেশ যেমন ছিল তেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যা প্রায় অসম্ভব।
একজন মানুষ হয়ত দেখতে একটা শিং মাছ বা টাইরানোসোরাস রেক্স ডায়নোসরের মতো নয়, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে গভীর পর্যবেক্ষণে আমরা দেখতে পাব, সব প্রাণীর দেহ প্রায় একই রকম জীবন্ত প্রাণকোষ দিয়ে গঠিত। এমনকি বৃক্ষ, লতাপাতা, অণুজীব বা মাশরুম ইত্যাদি একই উপাদানে তৈরি। আর পৃথিবীর বেশিরভাগ প্রাণীই আণুবীক্ষণিক; যাদের প্রায় সবাই একটি মাত্র প্রাণকোষ দিয়ে গঠিত। ব্যাকটেরিয়া এককোষী প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত, সংখ্যায় বেশি এবং পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়।
২০১৬ সালের এপ্রিলে বিজ্ঞানীরা এক সেমিনারে ‘প্রাণের বংশলতিকার’ সর্বশেষ আধুনিক সংস্করণ উপস্থাপন করেন; যেখানে সব ধরনের জীবিত প্রাণীকে বংশলতিকায় ভিন্ন ভিন্ন পর্বের মাধ্যমে দেখানো হয়। প্রাণীপর্বের প্রায় সব শাখাতেই ব্যাকটেরিয়ার আধিক্য। ফলে প্রাণীর বংশলতিকা দেখে মনে হয় সব জীবের আদিপিতা হলো ব্যাকটেরিয়া। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিটি জীবিত প্রাণ এমনকি আপনি নিজেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়ার বংশধর।
বিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে আমরা এখন প্রাণের উৎস কোথায় এই প্রশ্নের আরও যথাযথ উত্তর নিশ্চিত করতে পারব হয়ত। কিন্তু কীভাবে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হলো, তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে গেলে তথা কৃত্রিমভাবে একটা প্রাণকোষ তৈরি করতে আমাদের প্রয়োজন হবে ৩৫০-৪০০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক উপাদান এবং সে সময়কার প্রাথমিক প্রাণ বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশটিও হুবহু সৃষ্টি করতে হবে গবেষণাগারে। তাহলে একবার ভাবুন তো প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল কীভাবে তা প্রমাণ করা কতটা দুরূহ ব্যাপার?
প্রাথমিক পরীক্ষণ
প্রায় সমগ্র মানব ইতিহাসজুড়েই পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ কীভাবে শুরু হয়েছিল, এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনীয়তা কখনও বিবেচিত হয়নি। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে- উত্তর তো আগে থেকেই ধর্মতত্ত্বের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ছিল। এমনকি ১৮০০ শতকের আগে বেশিরভাগ বিজ্ঞানীও ‘প্রাণবাদে’ (Vitalism) বিশ্বাস করতেন। প্রাণবাদ মতে ধারণা করা হতো, প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে রয়েছে এমন কোনো ‘অলৌকিক’ উপাদান, যা তাদেরকে জড় বস্তু থেকে আলাদা করেছে, যা হয়তো সৃষ্টিকর্তার দান। এই মতবাদ অনেক সময় ধর্মতত্ত্বের সঙ্গেও গাঁটছড়া বাঁধত। ধর্মতত্ত্ব মতে, প্রথম মানবকে প্রাণদান করতে ঈশ্বর তার মুখে ফুঁ দিয়েছিলেন। আর চির অমর আত্মা প্রাণীর দেহে অলৌকিকভাবেই বিরাজিত থাকে।
এরপর ১৮ শতকের শুরুর দিকে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু বস্তুর সন্ধান পেলেন যেগুলোকে মনে হচ্ছিল প্রাণের জন্য অনন্য উপাদান। সেইসব উপাদানের মধ্যে ইউরিয়া অন্যতম; যা পাওয়া গিয়েছিল মূত্রের মধ্যে এবং তা ১৭৯৯ সালে প্রথম শনাক্ত করা সম্ভব হয়। বিজ্ঞানীরা তখন পর্যন্ত জানতেন, শুধু জীবিত প্রাণীর দেহেই এই ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারে। ফলে ধারণা করা হয় ইউরিয়া এবং ওইসব বস্তুর মধ্যেই হয়ত প্রাণের শক্তি সঞ্চিত আছে। যে কারণে সেই বস্তুগুলোকেও মনে করা হতো অন্যদের তুলনায় বিশেষ কিছু বা অতিপ্রাকৃত, যেগুলো প্রাণীদেহ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। তখন পর্যন্ত প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানের যা কিছু অর্জন ছিল তা প্রাণের অলৌকিকতার ধারণার সঙ্গেই বেশি মানানসই।
তবে ১৮২৮ সালে জার্মান রসায়নবিদ ফ্রেডরিখ ভোলার একটা সাধারণ রাসায়নিক দ্রব্য অ্যামোনিয়াম সায়ানেট থেকে ইউরিয়া উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। এই পদ্ধতির সঙ্গে জীবিত প্রাণীর কোনো যোগসূত্র ছিল না। অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও এগিয়ে এলেন ফ্রেডরিখ ভোলারের পথ অনুসরণ করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, প্রাণের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, এমন সাধারণ নিরীহ রাসায়নিক দ্রব্য থেকেও প্রাণের উপাদান তৈরি করা সম্ভব।
বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রাণ বিকাশে অলৌকিকতার স্থান এখানেই শেষ। কারণ, তখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, প্রাণের উপাদানগুলো একেবারেই বস্তুজগতীয় জিনিস। এর উৎস অবস্তুগত আত্মা বা অতিপ্রাকৃত কোনো স্বত্তা নয়। প্রণীদেহের বাইরের চারপাশের বস্তুজগতেও প্রাণের উপাদান রয়েছে। এবং মানুষসহ সব প্রাণী সম্ভবত সেই বস্তুজগত থেকেই আবির্ভূত হয়েছে।
বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রাণ বিকাশে অলৌকিকতার স্থানের সমাপ্তি ঘটে এখানেই । কিন্তু মানুষ তার মনের গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রাণ বিকাশের ঐশ্বরিক ধারণা এত সহজে দূর করতে পারে না। অনেকেই বলতে থাকেন, রসায়ন থেকে প্রাণ সৃষ্টির মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই বরং তাদের কাছে মনে হয় তা প্রাণকে এর ম্যাজিক থেকে বঞ্চিত করেছে, আর আমরা যেন যন্ত্র।
এমনকি বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত প্রাণের অলৌকিকত্বকে রক্ষা করতে রীতিমত মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন। উদাহরণত ১৯১৩ সালের শেষ নাগাদ ব্রিটিশ জৈবরসায়নবিদ বেঞ্জামিন মূর ‘জৈব শক্তি’ (Biotic Energy) নামে একটা তত্ত্বের অবতারণা করেন, যেটা আসলে নতুন মোড়কে প্রাণের অলৌকিকতা প্রচারের প্রবল চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। বেঞ্জামিন মূরের ‘জৈব শক্তি’ তত্ত্বে আবেগের প্রাধান্যও যথেষ্ট লক্ষ্যণীয় ছিল। বর্তমানে মূরের ‘জৈব শক্তি’ তত্ত্ব অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, এমন অনেক সায়েন্স ফিকশন আছে যেগুলোতে দেখানো হয় একজন মানুষের জীবনীশক্তি বাড়ানো সম্ভব অথবা নিঃশেষ করে দেয়া সম্ভব। উদাহরণত ‘ডক্টর হু’ এর একটা চরিত্র টাইম লর্ডস; যিনি পুনর্জন্ম শক্তি (regeneration energy) ব্যবহার করে বারবার জন্ম লাভ করছেন।
এমনকি যেখানে দেখানো হয়, তার জীবনী শক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তা বাড়ানোও হচ্ছে; যা ফের শীর্ষেও পৌঁছে যাচ্ছে। এই বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহিনিকে অভিনব মনে হলেও বাস্তবে এটা সেই পুরোনো ধারণারই নতুনভাবে উপস্থাপন মাত্র।
১৮২৮ সালের ওই আবিষ্কারের পর থেকেই প্রথম প্রাণের বিকাশ কীভাবে ঘটেছিলে তার বস্তুগত ব্যাখ্যা খুঁজতে থাকেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু তারা কোনো উপায়ান্তর খুঁজে পেলেন না। বিজ্ঞানীরা হয়তো তাদের প্রাণের অলৌকিকত্বের ধারণা থেকে সহজেই বের হতে পারছিলেন না।
এই ক্ষেত্রে বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে সবচেয়ে বড় যুগান্তকারী ধারণাটি দিলেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন। ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন ব্যাখ্যা করে দেখালেন কীভাবে এই বিপুলা পৃথিবীর ততধিক বিপুল পরিমাণ বিচিত্র প্রাণী জগতের উদ্ভব হয়েছে হয়ত একটা সাধারণ এককোষের আদিপিতা-মাতা থেকে।
এই প্রথম কেউ বললেন কোনো ঈশ্বর প্রতিটি জীবকে আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেননি। প্রাণিজগৎ সৃষ্টি হয়েছে কোটি কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর প্রাথমিক জৈব-রাসায়নিক উপাদান থেকে উৎপন্ন আদি প্রাণ থেকে। প্রাণী জগতের সবাই সেই আদি এককোষী প্রাণীর বংশধর।
চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব চারিদিকে বিতর্কের হইচই ফেলে দিল। ডারউইন এবং তার বিবর্তনবাদ ভয়ানক হিংস্র আক্রমণের শিকার হলো। অথচ বিবর্তনবাদের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি কীভাবে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি।
ডারউইন জানতেন প্রশ্নটা অতীব গুরুতর, কিন্তু তিনি যথাসম্ভব সতর্কভাবে শুরু করেছিলেন তবুও চার্চের সঙ্গ দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হলো না। পরে অবশ্য ১৮৭১ সালে লেখা এক চিঠিতে আবেগমথিত ভাষায় ডারউইন বলতে চেয়েছিলেন, প্রাণের উৎপত্তি কীভাবে এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর তিনি জানতেন। প্রাণের উৎপত্তি একটা ছোট উষ্ণ পুকুরে। যেখানে ছিল পর্যাপ্ত অ্যামোনিয়া এবং ফসফরাস লবণ। সেই সঙ্গে আলো, উত্তাপ, বিদ্যুৎ এবং রাসায়নিকভাবে স্বয়ং উদ্ভূত প্রোটিনের (আমিষের) জটিলযৌগ, যা আরও জটিল পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়ে প্রাণে পরিণত হয়।
ভিন্নভাবে বলা যেতে পারে, কী ঘটতে পারে যখন দীর্ঘদিন সাধারণ জৈব উপাদান পূর্ণ একটা ছোট জলাভূমি সূর্যালোকে ছিল? কিছু জৈব উপাদান হয়ত মিলেমিশে প্রাণের সদৃশ কোনো বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল আমিষ এবং আমিষ আরও জটিল কোনো বস্তুতে পরিণত হচ্ছিল। হতে পারে অস্পষ্ট ধারণামাত্র। কিন্তু ভবিষ্যতে এই অস্পষ্ট ধারণার উপর ভিত্তি করেই প্রাণের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রথম তত্ত্বটি দাঁড়িয়ে যায়।
এই তত্ত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত একটি স্থানে। আপনি হয়ত ভাবতে পারেন ঈশ্বরবিহীন প্রাণের উৎপত্তির মত সাহসী চিন্তা বিকশিত হয়েছে একটা গণতান্ত্রিক দেশে, যেখানে মানুষের বাক স্বাধীনতা সামাজিক ঐতিহ্যের অংশ। তা হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র? কিন্তু না, বাস্তব ঘটনা হলো অলৌকিকতাকে পাশ কাটিয়ে প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে প্রথম তত্ত্বটি বিকশিত হয় নিষ্ঠুরভাবে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে। যেখানে মুক্তচিন্তা ছিল নিষিদ্ধ। তখন স্ট্যালিনের রাশিয়াতে সবকিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। মানুষের চিন্তা, এমনকি জীববিজ্ঞানের মতো পঠন পাঠনের বিষয়ও, যা কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, সেটাও ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন।
সবচেয় আলোচিত ঘটনা ছিল, স্ট্যালিন জীনতত্ত্বের প্রচলিত পঠন পাঠনের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের আরেক জীববিজ্ঞানী এবং কৃষিবিদ ট্রোফিম ডেনিশোভিচ লিসেঙ্কো জোসেফ মেন্ডেলের জিনতত্ত্ব এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদকে বাতিল করে বংশপরম্পরার উপর জোর দেন। তিনি মনে করতেন, প্রাণী তার জীবনের অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে সঞ্চারিত করে যায়। লিসেঙ্কো দেখালেন উন্নতজাতের গম থেকে উন্নত এবং অধিকফলনশীল গম কীভাবে উৎপাদন করা যায়। স্ট্যালিন কমিউনিস্ট ভাবধারার সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ ট্রোফিম ডেনিশোভিচ লিসেঙ্কোর মতবাদকে চাপিয়ে দেন। জীনতত্ত্ব বা বংশগতিবিদ্যা নিয়ে যেসব বিজ্ঞানীরা কাজ করছিলেন তাদেরকে জনসাধারণের কাছে লিসেঙ্কোর মতবাদকে সমর্থন এবং প্রচার করতে বাধ্য করা হয়। অন্যথায় তাদের স্থান হতো লেবার ক্যাম্পে।
স্ট্যালিনের দমন নিপীড়নের শাসনের মধ্যেই আলেক্সান্ডার ওপারিন চালিয়ে যেতে লাগলেন তার জৈবরাসায়নিক গবেষণা। ওপারিন নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কারণ, তার কমিউনিজমের প্রতি সন্দেহাতীত আনুগত্য ছিল। তবে বংশগতির ক্ষেত্রে ওপারিন লিসেঙ্কোর তত্ত্বকে সমর্থন দেন এবং দেশের সেবা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের ‘অর্ডার অফ লেনিন’ নামের সর্বোচ্চ পুরষ্কারে ভূষিত হন।
১৯২৪ সালে আলেক্সান্ডার ওপারিন প্রকাশ করলেন ‘দ্য অরিজিন অফ লাইফ’ নামে তার অমর গ্রন্থখানি। এতে ওপারিন প্রাণের বিকাশ সন্ধানে যে প্রস্তাবনা হাজির করেন সেটা ডারউইনের বিবর্তনবাদের ‘একটি ছোট্ট উষ্ণ পুকুরে প্রাণের উৎপত্তি’ ধারণার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায়।
ওপারিন কল্পনা করেছিলেন কেমন ছিল সদ্য গঠিত পৃথিবীর চেহারা। পৃথিবীর উপরিভাগ ছিল কল্পনাতীত গরম। মহাকাশ থেকে খসে পড়ছিল জ্বলন্ত পাথরের খণ্ড। পৃথিবী তখন ছিল বিভিন্ন ধরনের বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থমিশ্রিত অর্ধগলিত পাথরের বিশৃঙ্খল স্তুপ। পদার্থগুলোর মধ্যে কার্বনের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি।
ধীরে ধীরে উত্তপ্ত পৃথিবী ঠান্ডা হলো, জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে প্রথম বৃষ্টি নামল পৃথিবীর বুকে, তরল পানিতে তলিয়ে গেল চরাচর। বৃষ্টি পড়ার আগেও সমুদ্র ছিল। কিন্তু সেটা ছিলো প্রচণ্ড উত্তাপে গলিত কার্বননির্ভর ঘন তরল।
এমতাবস্থায় দুইটা ব্যাপার ঘটতে পারে। প্রথমত. বিভিন্ন রাসায়নিক নিজেদের মাঝে বিক্রিয়া করে অসংখ্য নতুন জটিল যৌগ সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মধ্যে কিছু যৌগ আরও জটিল যৌগে পরিণত হবে। আলেক্সান্ডার ওপারিন ধারণা করেন, রাসায়নিক দ্রবণের ক্ষুদ্র মৌলগুলি প্রাণের দিকে ধাবিত হয়। প্রসঙ্গত, প্রাণের দুটো মৌলিক উপাদান চিনি (Sugar) এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড পৃথিবীর পানি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।
দ্বিতীয়ত. কিছু রাসায়নিক দ্রব্য নতুন আণুবীক্ষণিক অণুজীবের কাঠামো তৈরি করতে শুরু করে। কিছু অণুজীবের জৈবরাসায়নিক উপাদান পানিতে দ্রবীভূত হয় না। যেমন তেল পানির উপর আস্তরণ সৃষ্টি করে ভেসে থাকে। কিন্তু যখন কিছু জৈবরাসায়নিক উপাদান পানির সঙ্গে মিশে যায় তখন গোলাকার ‘কোয়াসারভেটিভ’ নামক বস্তুর রূপ ধারণ করে যেগুলো আয়তনে .০১ সেমি বা (.০০৪) ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। যেগুলো জীবন্ত কোষের মতো বেড়ে ওঠে। অবয়ব পরিবর্তন করে এমনকি মাঝেমধ্যে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তারা চারপাশের পানির রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। ফলে প্রাণসদৃশ রাসায়নিক উপাদান তাদের মাঝে সংগঠিত হতে থাকে। ওপারিন প্রস্তাব করেন এই কোয়াসারভেটিভ হলো আধুনিক জীবিত কোষের পূর্বপুরুষ।
এর পাঁচ বছর পরে ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী জন বারডন স্যান্ডারসন হালডেন একই মতবাদ নিয়ে র্যাশনালিস্ট অ্যানুয়াল জার্নালে একটা ছোট প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। হালডেন ইতিমধ্যেই বিবর্তনবাদে প্রভূত অবদান রেখে ফেলেছেন। তিনি ডারউইনের মতবাদকে বিকাশমান জীনতত্ত্বের আলোকে আরও সংহত করেন।
হালডেন ছিলেন তার জীবনের থেকেও বড় এক চরিত্র। একবার ডিকম্প্রেসন চেম্বারের কিছু পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তার কানের পর্দায় ছিদ্র হয়ে যায়। কিন্তু পরে তিনি রম্য করে লিখেছিলেন, ‘কানের পর্দা সাধারণত প্রাকৃতিকভাবেই সুস্থ হয়ে যায়। যদি পর্দায় ছিদ্র থেকেই যায় এবং তারফলে কেউ যদি বধির হয়ে যায় তাহলে সে কারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই কান দিয়ে বাতাসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে পারবে, যেটা হবে একটা সামাজিক অর্জন!’
ওপারিনের মতো হালডেনও বললেন, সমুদ্র প্রাথমিক অবস্থা থেকে স্থিতিশীল গরম ঘন তরলে পরিণত হলে কীভাবে সেখানকার পানিতে রাসায়নিক অনুজীব নিজে থেকেই সৃষ্টি হতে পারে। পৃথিবীর এরকম পরিবেশে প্রথম জন্ম নেয় প্রাণের অণুজীব অথবা অর্ধজীবন্ত বস্তু আর এরপরের স্তরে সৃষ্টি হয় স্বচ্ছ তেলতেলে জেলির মত থকথকে প্রাণবস্তু।
কথিত আছে, ওপারিন এবং হালডেন যে তত্ত্বের অবতারণা করেন পৃথিবীর সমস্ত জীববিজ্ঞানী সেগুলো পুনর্ব্যক্ত করেন মাত্র। প্রাণের প্রথম বিকাশ ঘটেছে পুরোপুরি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এবং এতে কোনো ঈশ্বরের হাত নেই বা এতে কোনো আগাম প্রাণশক্তিরও ভুমিকা ছিল না। এই ধারণাটিও ডারউইনের বিবর্তনবাদের মতোই ছিল বিপ্লবী। এই তত্ত্বও ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিমূলে চরম কুঠারাঘাত করল।
ঈশ্বরবিহীন সৃষ্টিতত্ত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনো সমস্যা ছিল না। কারণ, কমিউনিস্ট শাসিত সোভিয়েত রাষ্ট্রীয়ভাবেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। সে জন্যই কমিউনিস্ট নেতারা প্রাণের উৎপত্তি গবেষণায় এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। হালডেন নিজেও ছিলেন একজন নাস্তিক এবং কমিউনিজমের কড়া সমর্থকও ছিলেন।
সে সময়ে সাধারণত বামপন্থি এবং কমিউনিস্ট চিন্তা ধারার লোকজন এই ঈশ্বরবিহীন প্রাণ সৃষ্টির ধারণা মেনে নিত। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে এই তত্ত্ব বেশ সাদরেই গৃহীত হলো। আর ইউরোপ-আমেরিকায়ও যারা এই তত্ত্ব মেনে নিয়েছিলো তারাও ছিলো বামপন্থি বা কমিউনিস্ট ভাবধারার লোকজন।
প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে আদিম জৈবরাসায়নিক ঘন তরল সহযোগে- এই ধারণাটি ওপারিন-হালডেন তত্ত্ব বলে ব্যাপক পরিচিত পেয়ে গেল। ওপারিন-হালডেন তত্ত্ব যুক্তির বিচারে গ্রহণযোগ্য হলেও তত্ত্বটির একটা সমস্যা ছিল। ওপারিন-হালডেন তত্ত্বকেও নির্ভুল করার স্বপক্ষে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণালব্ধ প্রমাণ ছিলো না। ২৫ বছর পার হয়ে গেলেও তত্ত্বটির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ দাঁড় করানো যায়নি।
সময়ের সঙ্গে প্রাণের উৎপত্তির রহস্য সমাধানের গবেষণায় যোগ দেন ১৯৩৪ সালে রসায়নে নোবেল বিজয়ী আমেরিকান রসায়নবিদ হ্যারল্ড উরে। তিনি পারমাণবিক বোমা বানানোর দলেও কাজ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ম্যানহাটান প্রকল্পে পারমাণবিক বোমার অতি প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম-২৩৫ সংগ্রহ করতেন তিনি। যুদ্ধের পরে তিনি পরমাণু প্রযুক্তিকে সাধারণ জনগণের সমাজের নিয়ন্ত্রণে দেয়ার জন্য আন্দোলন করেন।
প্রফেসর উরে ধারণা করেছিলেন, আমাদের পৃথিবী আদিম অবস্থায় সম্ভবত অ্যামোনিয়া, মিথেন এবং হাইড্রোজেনের মিশেলে পিণ্ডাকৃতির ছিল। এই মিশ্রণকে যদি বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণ এবং পানির সংস্পর্শে আনা যায় তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপন্ন করা সম্ভব। এটা সর্বজনবিদিত যে, অ্যামাইনো অ্যাসিড হলো প্রাণের প্রথম উপাদান।
উরে এই সময়ে পৃথিবীর বাইরে মহাকাশ এবং মহাকাশের ভাসমান বস্তুকণার রসায়ন নিয়ে আগ্রহী হন। বিশেষকরে দেখতে চেয়েছিলেন সৌরজগৎ যখন সবে সৃষ্টি হলো, তখন ঠিক কী ঘটছিল। একদিন তিনি ক্লাসে বললেন, সৃষ্টিলগ্নে পৃথিবীর বায়ুস্তরে সম্ভবত অক্সিজেনের অস্তিত্ব ছিল না। অক্সিজেন না থাকার কারণেই ওপারিন এবং হালডেনের তত্ত্বে প্রস্তাবিত আদিম জৈবরাসায়নিক ঘন তরলটি তৈরি হতে পেরেছিল। কেননা অক্সিজেন থাকলে তার সংস্পর্শে এসে ভঙ্গুর রাসায়নিকগুলো পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যেত।
প্রফেসর হ্যারল্ড উরের ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন পিএইচডির গবেষণারত ছাত্র স্ট্যানলি মিলার। তিনি উরেকে প্রস্তাব দেন পরীক্ষা করে দেখার জন্য আসলেই কেমন ছিল সেদিনের পৃথিবীর পরিবেশ। উরে নিজের ধারণার উপর কিছুটা সন্দেহ পোষণ করলেও মিলার অক্সিজেনহীন পৃথিবীর চিন্তায় তাকে আরও মনোনিবেশ করালেন। তাদের মাঝে বিস্তর আলোচনার পরে ১৯৫২ সালে প্রফেসর উরে এবং তার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্ট্যানলি লয়েড মিলার যৌথভাবে প্রথমবারের মত প্রাণের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল তার খোঁজে বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত ‘উরে-মিলার এক্সপেরিমেন্ট’ শিরোনামে একটি পরীক্ষা শুরু করলেন।
পরীক্ষার যন্ত্রপাতি খুব সাধারণ ছিল। মিলার পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্নের চারটি রাসায়নিক উপাদান- গরম পানি, হাইড্রোজেন গ্যাস, অ্যামোনিয়া এবং মিথেন, চারটি কাচের জারে ভরে তাদের মাঝে সংযোগ স্থাপন করে দিলেন। কাচের জারের মাঝে মিলার বারবার তড়িৎপ্রবাহ দিতে লাগলেন যাতে বজ্রপাত ঘটে। আদিকালে পৃথিবীতে বজ্রপাতের ঘটনা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক। এই পরীক্ষার মাধ্যমে খুব সাধারণ পরিবেশেই প্রচুর পরিমাণ জৈব অনু উৎপাদন সম্ভব। মিলার দেখতে পেলেন প্রথমদিনেই কাচের জারের মধ্যকার দ্রবণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গোলাপী আভা ধারণ করেছে এবং সপ্তাহ শেষে ঘন তরল দ্রবণটি গাঢ় লাল হয়ে গেল। পরিষ্কার বোঝা গেল জারে জৈব রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ তৈরি হয়েছে।
মিলার পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে মিশ্রণটিতে গ্লাইসিন এবং আলানাইন নামে দুইটা অ্যামাইনো অ্যাসিড পেলেন। অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো হলো প্রাণের প্রাথমিক উপাদান। অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রোটিন (আমিষ) সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এই অ্যাসিড আমাদের শরীরের শারীরবৃত্তিক এবং জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মিলার গবেষণাগারে জন্ম দিলেন প্রাণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে প্রাণ আরও জটিল, আমরা যতটা ভাবি তার থেকেও বেশি।
এই গবেষণার ফলাফল বিখ্যাত সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হলো ১৯৫৩ সালে। প্রাণের উৎপত্তির রহস্য সমাধানের অভিযানে ‘উরে-মিলার এক্সপেরিমেন্ট’ এক স্মরণীয় ঘটনা। প্রফেসর উরে এই গবেষণার পুরো কৃতিত্ব মিলারকে দিলেন এবং আর্টিকেল থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। তবুও এই পরীক্ষা ‘উরে-মিলার এক্সপেরিমেন্ট’ হিসেবেই ইতিহাসে উচ্চারিত হয়।
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীব বিজ্ঞানের গবেষক জন সাদারল্যান্ড বলেন, ‘উরে-মিলার পরীক্ষার গুরুত্ব এখানেই যে, এখন প্রমাণ হলো আপনি সাধারণ পরিবেশেও কোনো প্রাণীদেহের সংস্পর্শ ছাড়াই প্রচুর অণুজীব সৃষ্টি করতে পারবেন।’
কিন্তু পরবর্তীতে আরও গবেষণায় পৃথিবী সৃষ্টির আদিতে অন্যান্য গ্যাসের মিশ্রণও ছিল, এমন আবিষ্কারের কারণে আগের গবেষণা ভুল প্রমাণ হয়। কিন্তু সেটা ভিন্ন আলোচনার বিষয়। জন সাদারল্যান্ড বলেন, ‘উরে-মিলার পরীক্ষা ছিল দৃষ্টান্তমূলক, তারা মানুষের কল্পনা জাগাতে পেরেছিলেন এবং এরপর প্রাণের উৎস সন্ধানের বিষয়টি নিয়ে লোকে ব্যাপকভাবে আলাপ-আলোচনা শুরু করে।’
মিলারের পরীক্ষার প্রভাবে অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও এগিয়ে এলেন ভিন্ন ভিন্ন মৌল থেকে অনুজীব সৃষ্টির গবেষণা করে প্রাণের উৎসের সন্ধানে। প্রাণের সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনের হাতছানি মনে হলো সন্নিকটে।
এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গেছে প্রাণ এত জটিল যে, তা আমরা চিন্তা করতেও সক্ষম নই। জীবন্ত কোষ শুধুমাত্র কিছু রসায়নের জটিল যৌগ নয় বরং এক সূক্ষ্ম শিল্পিত যন্ত্রবিশেষ। যা হঠাৎ করেই সম্পর্কহীন বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়ে বিজ্ঞানীদের সামনে ধারণার চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়।
[পরের পর্বে থাকছে ডিএনএ আবিষ্কারে যেভাবে পাল্টে বিজ্ঞানীদের চিন্তার জগত।]
আরও পড়ুন:‘সূর্যই ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে’, আমানতের দাবি কেন ভুল
‘ক্রিস্টাল পৃথিবীতে’ ব্যাখ্যাতীত সব রহস্যের সমাধান!
ভূত্বক গঠন হতে পারে ধারণারও ৫০ কোটি বছর আগে
- ট্যাগ:
- পৃথিবী











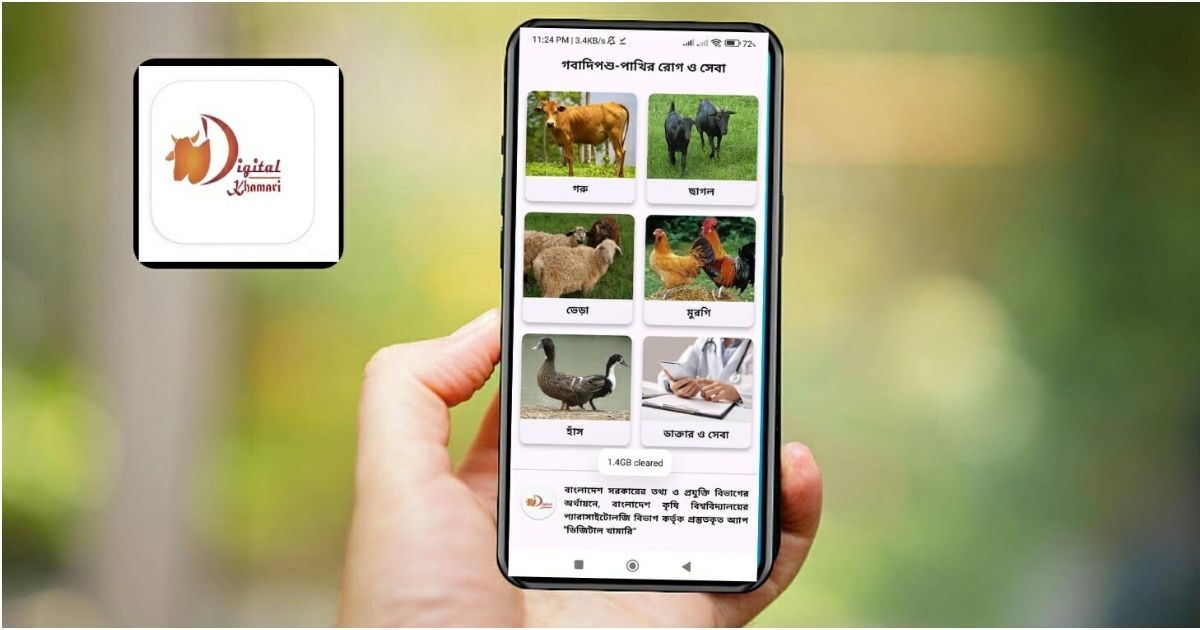
মন্তব্য