এবার মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চারে সক্ষম হলেন বিজ্ঞানীরা। আর এমনটি ঘটিয়েছেন ইয়েল ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক।
নেচারে প্রকাশিত এক জার্নালে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ মেডিসিনের বিজ্ঞানীরা এই অসাধ্য সাধন করেছেন।
বিজ্ঞানীরা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে শূকরের মৃত্যুর ১ ঘণ্টা পর সেই মৃত শূকরের দেহে রক্ত সঞ্চালন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং অনেক কোষেরই কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করেছেন।
শুরুতে গবেষকরা অচেতন একটি শূকরের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দেন, ফলে তার শরীরের কোষগুলোতে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে মারা যায়।
শূকরের মৃত্যুর ১ ঘণ্টা পর ওরগানইএক্স নামের নতুন এক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার চিকিৎসা শুরু হয়। এতে মৃত শূকরের শরীরে পুনরায় রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়। এমনকি সেই শূকরের হৃৎপিণ্ডর কার্যকারিতাও শুরু হয়, সচল হয় কিডনি ও লিভারও। হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের সরাসরি প্রমাণও পাওয়া গেছে।
গবেষকরা শূকরটির মৃত্যুর ৬ ঘণ্টা পরেও সাড়া পেয়েছেন। শূকরটি তার কাঁধও ঝাঁকিয়েছে। যদিও কাঁধ ঝাঁকানোর বিষয়টির গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বিজ্ঞানীরা।
ইয়েল ইউনিভার্সিটির কমপারাটিভ মেডিসিন, জেনেটিক্স ও মনোরোগবিদ্যার অধ্যাপক এবং ন্যাচারে প্রকাশিত গবেষণার সহলেখক নেনাদ সেস্তান বলেছেন, ‘আমরা শরীরজুড়ে (মৃত শূকরের) রক্ত সঞ্চালন পুনরায় চালু করতে সক্ষম হয়েছি; যা আমাদের নিজেদেরই বিস্মিত করেছে।’
মৃত শূকরের ক্ষেত্রে এমন সাফল্যে উচ্ছসিত বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রযুক্তি অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। এমনকি মৃত্যু বলতে আমাদের স্বাভাবিক ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলবে।
নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির গ্রসম্যান স্কুল অফ মেডিসিনের ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড রিসাসিটেশন রিসার্চের পরিচালক স্যাম পার্নিয়া বলেন, ‘এই গবেষণাটি প্রমাণ করে যে মৃত্যুসংক্রান্ত আমাদের সামাজিক ধারণা অর্থাৎ জীবিত অথবা মৃত তার বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই। বিপরীতে, বৈজ্ঞানিকভাবে মৃত্যু হলো একটি জৈবিক প্রক্রিয়া, যা ঘটার কয়েক ঘণ্টা পরও চিকিৎসাযোগ্য।’
তবে নতুন এই গবেষণা কিছু নৈতিক প্রশ্নও সামনে আনছে। ঠিক কখন একজন ব্যক্তিকে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করতে পারবেন, তা এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে অবস্থাকে মৃত বলা হচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই সেই অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব, কারণ দেহের সব কোষ একসঙ্গে মারা যায় না।
মৃত শূকরের দেহে প্রাণ সঞ্চারকারী ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষক দল এর আগে ২০১৯ সালে একটি শূকরের মস্তিষ্ককে দেহ ছাড়াই প্রায় ঘণ্টাখানেক বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।
আরও পড়ুন:মানুষের নিউরন কম্পিউটার প্রসেসরে
রাতভর মানুষের মুখের ওপর কিলবিল করে যারা
- ট্যাগ:
- বিজ্ঞান

 মো: ইমরানুর রহমান
মো: ইমরানুর রহমান

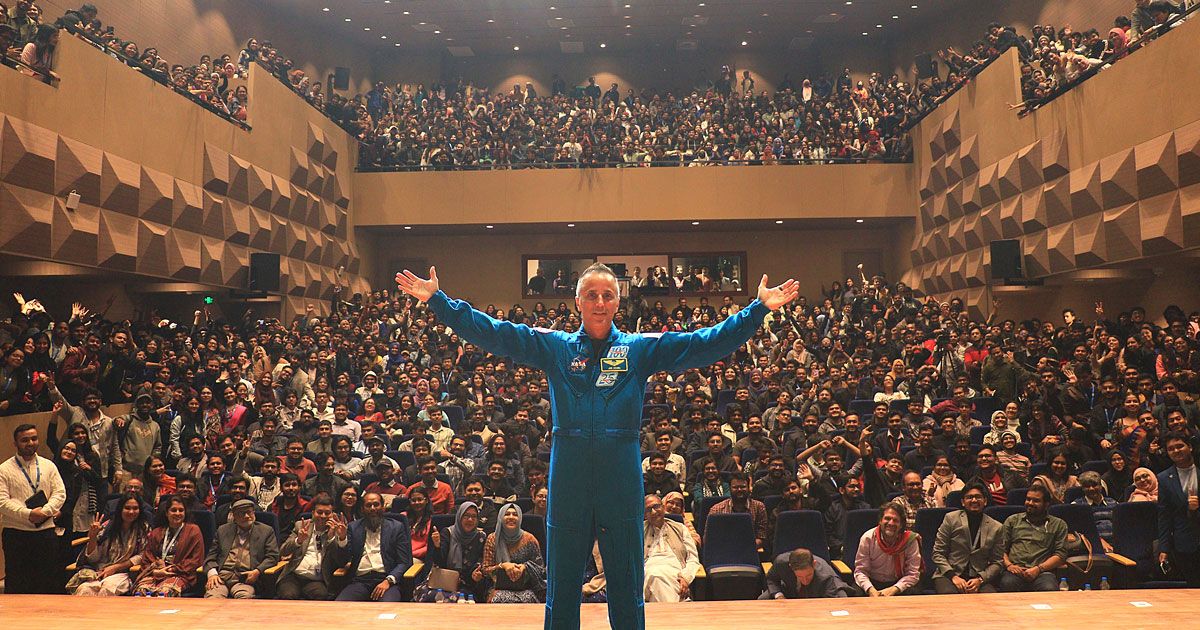








 পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়া দুই গবেষক জন জে. হপফিল্ড ও জেফরি ই. হিন্টন। ছবি: নোবেল প্রাইজ আউটরিচ
পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়া দুই গবেষক জন জে. হপফিল্ড ও জেফরি ই. হিন্টন। ছবি: নোবেল প্রাইজ আউটরিচ
মন্তব্য