কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের একটি পুরনো সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা পদার্থের এমন এক নতুন দশা তৈরি করেছেন, যেখানে সময়ের দুটি মাত্রা বা ডাইমেনশন। পদার্থের এই দশা কঠিন, তরল ও বায়বীয় দশার চেয়ে ভিন্ন।
পরম তামপাত্রার (-৪৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট) কাছাকাছি তাপমাত্রায় কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের কাজ করে কিউবিট। একই সঙ্গে আশেপাশের বিদ্যুত ও চৌম্বক ক্ষেত্রকে এড়িয়ে তাদেরকে এ কাজটা করতে হয়।
বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবের কারণে কিউবিটের তথ্য প্রবাহে বিঘ্ন হয়। কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের এ ত্রুটিগুলো সারানোর পথ খুঁজে বের করাটাই বিজ্ঞানীদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।
কানাডার একদল বিজ্ঞানীর দাবি, তারা এ সমস্যা সমাধানের নতুন এক উপায় বের করেছেন। আর সেটা করতে গিয়ে তারা পদার্থের এমন এক দশা তৈরি করেছেন, যেখানে সময় একটি নয়, দুটি মাত্রা নিয়ে অস্তিত্বশীল।
এক প্রতিবেদনে এটি জানিয়েছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ভিত্তিক সাইট ভাইস। নিউজবাংলার পাঠকদের জন্য সেটির ভাষান্তর করেছেন রুবাইদ ইফতেখার।
নতুন এ আবিষ্কারের খবর প্রকাশিত হয়েছে নেচার জার্নালে, গত বুধবার। গবেষকদের অন্যতম সদস্য ও কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার পদার্থবিদ্যার শিক্ষক অ্যান্ড্রু পটার এক ই-মেইলে ভাইসকে জানিয়েছেন, ‘পদার্থের নতুন দশাকে নিয়ে তারা যে কাজ করেছেন, সেটা আমাদের পরিচিত কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থার চেয়ে ভিন্ন।
তিনি লেখেন, ‘পদার্থের দশাগুলি সম্পর্কে চিন্তা করার আধুনিক উপায় হল একটি দশাকে স্থিতিমাপের বিশেষ অঞ্চল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা, যেখানে পরিবর্তনের সম্মুখীন না হয়ে কোনো দশার টিকে থাকা সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে গলে তরলে পরিণত হয় না। এটা তখনই গলতে শুরু করে যখন এটা একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা অতিক্রম করে, যা ওই পদার্থের মেল্টিং পয়েন্ট।’
তাপমাত্রার কীভাবে পদার্থের দশায় পরিবর্তন ঘটায় সেটার চেয়ে পটার ও তার সহকর্মীরা দেখেছেন যে বস্তুর কোনো অবস্থায় সময় কীভাবে একটি সীমানা নির্ধারণ করে দিতে পারে। এ সীমানার ফলে যা সৃষ্টি হচ্ছে তাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, ‘ডাইনামিক টপোলজিক্যাল ফেজ’। এতে করে, তাপমাত্রার বদলে কোয়ান্টাম সিস্টেমের ভুলগুলো ফেজে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।
পটার যোগ করেন যে, এই দশায় তাদের সিস্টেমকে রেখে দলটি দেখিয়েছে যে তারা কিউবিটকে এক ধরণের ত্রুটি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এই অবস্থা ধরে রাখার জন্য কিউবিটগুলির এমন কিছু প্রয়োজন যা অসম্ভব শোনায়, আর তা হলো দ্বিমাত্রিক সময়।
এটি অর্জন করার লক্ষ্যে গবেষকরা প্রাচীন ও বিখ্যাত একটি গাণিতিক প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করেছেন– ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স। ১১ শতকে ইতালির গণিতবিদ ফিবোনাচ্চি প্রথম এটি উদ্ভাবন করেন। এ সিকোয়েন্স আসলে সংখ্যার এমন একটি ধারা যেখানে প্রতিটি সংখ্যা আগের দুই সংখ্যার যোগফল। প্রাকৃতিক অনেক বিষয় যেমন সূর্যমুখী ফুলের বিজের সর্পিল বিন্যাসে এ সিকোয়েন্স লক্ষ্য করা যায়।
তাদের গবেষণার জন্য পটার ও তার দল এ সিকোয়েন্সে সংখ্যাগুলোর অনুপাতের দিকে লক্ষ্য করেছেন ও বের করার চেষ্টা করেছেন কী করে তারা সিস্টেমে আটকে পড়া কিউবিটকে এ অনুপাতে লেসার ছুড়ে রক্ষা করতে পারেন।
পটার বলেন, ‘ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সে সংখ্যার পুনরাবৃত্তি নেই, আবার এটি কোনো দ্বৈবচয়ন ভিত্তিক ধারাও নয়। এর ফলে কার্যত আমরা সিস্টেমে সময়ের দুটো আলাদা মাত্রাকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছি।’
ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্সের ফলে একটি আপাত-পর্যায়ক্রমিক ছন্দ তৈরি হয়েছে, যার সঙ্গে কোয়াসিক্রিস্টাল নামক পদার্থের আরেক ধরণের অদ্ভূত দশার মিল রয়েছে। সাধারণ একটি ক্রিস্টালে শৃঙ্খলাবদ্ধ কাঠামো ও একই ধরণের কাঠামো (মৌচাক যেমন) দেখা যায়, কিন্তু কোয়াসিক্রিস্টালে শৃঙ্খলাবদ্ধ কাঠামো থাকলেও তাতে পুনরাবৃত্তি থাকে না। কারণ কোয়াসিক্রিস্টালগুলো আসলে অন্য কোনো উচ্চমাত্রায় চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া ১ বা ২ মাত্রার চেহারা।
ঠিক যেভাবে কোয়াসিক্রিস্টালগুলো তাদের বাড়তি মাত্রাগুলো লুকিয়ে ফেলতে পারে, গবেষকরা দেখেছেন ঠিক একই ভাবে ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স সময়ের ক্ষেত্রে একটা বাড়তি মাত্রা লুকিয়ে রাখতে সক্ষম।
পটার বলেন, ‘কার্যত এটি আমাদের সময়ের দুটো মাত্রাকে চিড়ে-চ্যাপ্টা করে সময়ের একটা নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করতে সহায়তা করে। আর এতে করে আমরা সার্বিকভাবে কিউবিটগুলোকে সুরক্ষা দিতে পারি।’
গবেষকরা তাদের এ পরীক্ষা কোয়ান্টাম কম্পিউটারে আটকে পড়া কিউবিটের ওপর করে দেখেছেন যে, ফিবোনাচ্চি সিকোয়েন্স ব্যবহার করা লেসার পালসগুলো পরীক্ষা চলাকালীন পুরো সময় (৫.৫ সেকেন্ড) কিউবিটগুলোকে স্থির রাখতে সক্ষম হয়েছে। সাধারণ লেসার পালসের ক্ষেত্রে এ সময়টা ১.৫ সেকেন্ড।
যদিও এ গবেষণা দিয়ে এখনই কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের সব ত্রুটি দূর করা যাবে না, তবে পটারের মতে কোনো পদ্ধতি ভবিষ্যতে কোয়ান্টাম মেমোরি ও কম্পিউটিংয়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে সেটার একটা ধারণা এ থেকে পাওয়া যায়।
তিনি বলেন, ‘এ পরীক্ষাগুলো থেকে অন্তত এটা প্রমাণ হয়েছে যে, ভুল আর গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণির ত্রুটির প্রতি সংবেদনশীল নয় এমন কোয়ান্টাম সিস্টেমকে নিজেদের কাজে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের উপায় রয়েছে। আমি আশাবাদী এটি দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর হতে পারে।’
উন্মোচিত হলো কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায়
যৌন মিলনের পর অনেকে কেন কাঁদেন?

 রুবাইদ ইফতেখার
রুবাইদ ইফতেখার






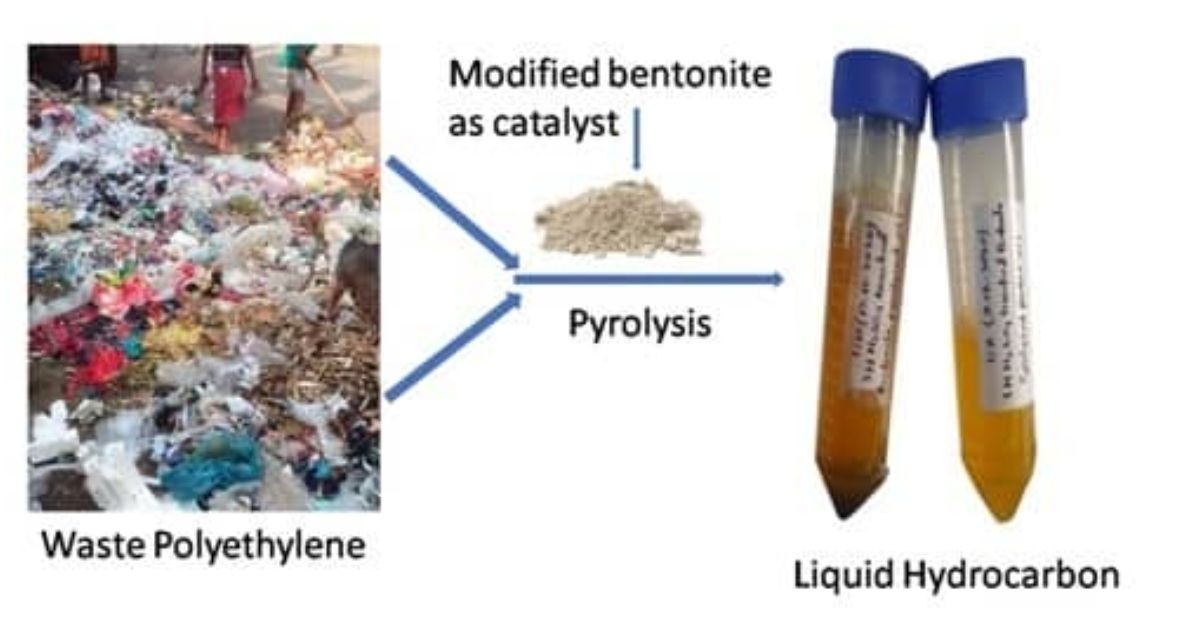

 সবুজ হোসেন
সবুজ হোসেন


 দেবাশীষ দেবু
দেবাশীষ দেবু মেহেরাবুল ইসলাম সৌদিপ
মেহেরাবুল ইসলাম সৌদিপ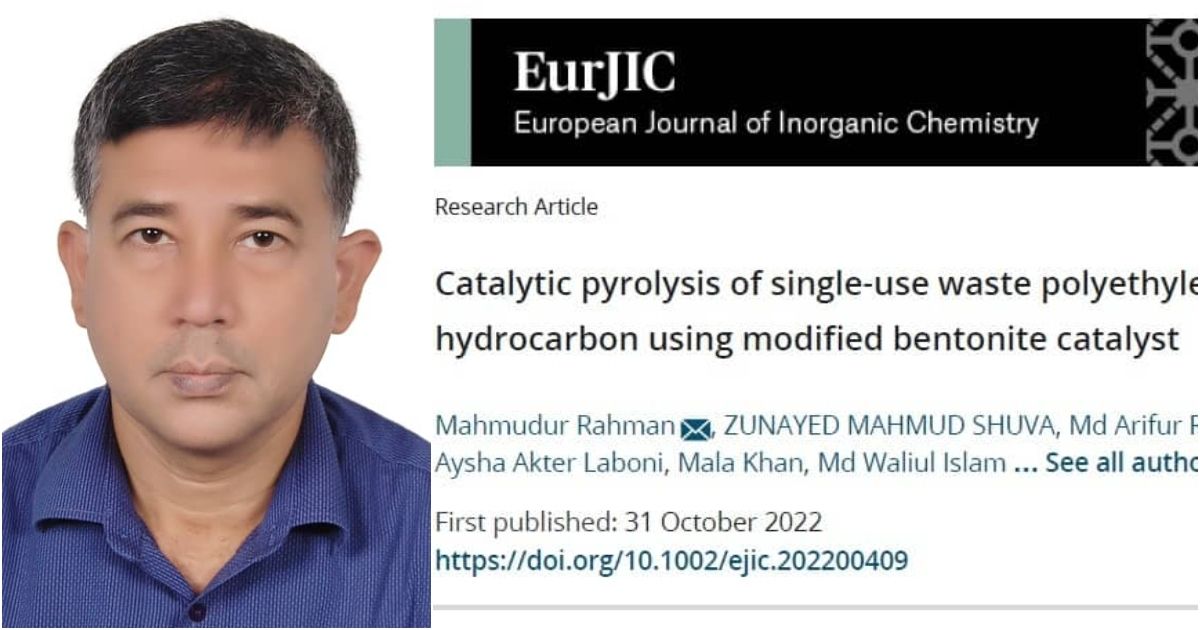
 মোশফেকুর রহমান
মোশফেকুর রহমান নারীর হাতে প্রোসথেটিক পদ্ধতির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে নাক তৈরি করা হয়। ছবি: তুলুজ ইউনিভার্সিটি হসপিটাল
নারীর হাতে প্রোসথেটিক পদ্ধতির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে নাক তৈরি করা হয়। ছবি: তুলুজ ইউনিভার্সিটি হসপিটাল
মন্তব্য