পেস্ট্রি, কফি, আইসক্রিমে চিনি তো থাকেই, এ যুগে ভিনদেশি খাবার খেয়ে দেখতে গেলে চিকেন কারিতেও সুগারের স্বাদ পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে চিনিকে আমরা বিশেষ স্বাদ হিসেবে ভাবতে না পারলেও একজন ডায়াবেটিকস রোগী কিন্তু হাড়ে হাড়ে সুগারের স্বাদ মিস করেন।
এবার কোনো সুগার মিলে নয়। সাগরের নিচে চিনির বিশাল মজুতের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এর আগে এমন কিছুর বিষয়ে কারও কোনো ধারণা ছিল না।
নেচারে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কার্বন সঞ্চয়ের কারণে সমুদ্রের তলদেশে যে সামুদ্রিক ঘাস রয়েছে, তার শেকড় থেকেই সৃষ্টি হয়ে নিচেই সুক্রোজ আকারে চিনি জমা হয়। যা রাইজোস্ফিয়ার নামে পরিচিত।
আমরা রান্নাবান্নার কাজে যে চিনি ব্যবহার করি তার প্রধান উপাদানই হলো সুক্রোজ। গবেষণায় দেখা গেছে সমুদ্রতলে চিনির ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় ৮০ গুণ বেশি।
গবেষকরা বলছেন, এই পৃথিবীতে সামুদ্রিক ঘাসের নিচে প্রায় ১.৩ মিলিয়ন টন সুক্রোজ থাকতে পারে। এটিকে অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, কোকা-কোলার প্রায় ৩২ বিলিয়ন ক্যানের জন্য এই চিনি যথেষ্ট।
কিন্তু এই চিনি আসলে সমুদ্রের তলে কীভাবে তৈরি হয়, তা নিয়ে জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর মেরিন মাইক্রোবায়োলজির সামুদ্রিক অণুজীববিদ নিকোল ডুবিলিয়ার বলেছেন, ‘সাগরের তলদেশের ঘাসগুলো সালোকসংশ্লেষণের সময় চিনি তৈরি করে।’
উদ্ভিদের পক্ষে যেহেতু শিকার করা কিংবা অন্য কোনো উপায়ে খাবার তৈরি করা সম্ভব হয় না, তাই সালোকসংশ্লেষণের সাহায্যেই সে তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপাদান তৈরি করে নেয়। এ পদ্ধতিতে গড় আলোর উপস্থিতিতে নিজস্ব বিপাক ও বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ বেশির ভাগ সুগার বা সুক্রোজ ব্যবহার করে।
কিন্তু বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের তলদেশের ঘাসগুলো আগের থেকে বেশি তাপমাত্রা ও আলো পাচ্ছে। ফলে তাদের প্রয়োজনের থেকে তারা বেশি পরিমাণ সুক্রোজ উৎপন্ন করছে।
সেই অতিরিক্ত সুক্রোজই সামুদ্রিক ঘাসগুলো রাইজোস্ফিয়ার আকারে ছেড়ে দেয়। যা ঘাসগুলোর গোড়ায় জমা হয়।
গবেষকরা বলছেন, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রতলে যে চিনি জমছে, বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তনে তার প্রভাব বুঝতে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।
আরও পড়ুন:কেরু ছাড়া সরকারি সব চিনিকল লোকসানে
দাম চড়া, দেশি চিনির দেখা মেলে না
‘জামাই আপ্যায়নের’ লাল চিনি
চালুর পরদিনই বন্ধ চিনিকল, বিপাকে আখচাষি
চাহিদার আখই পাচ্ছে না চিনিকল, গুনছে লোকসান
- ট্যাগ:
- চিনি

 মো: ইমরানুর রহমান
মো: ইমরানুর রহমান




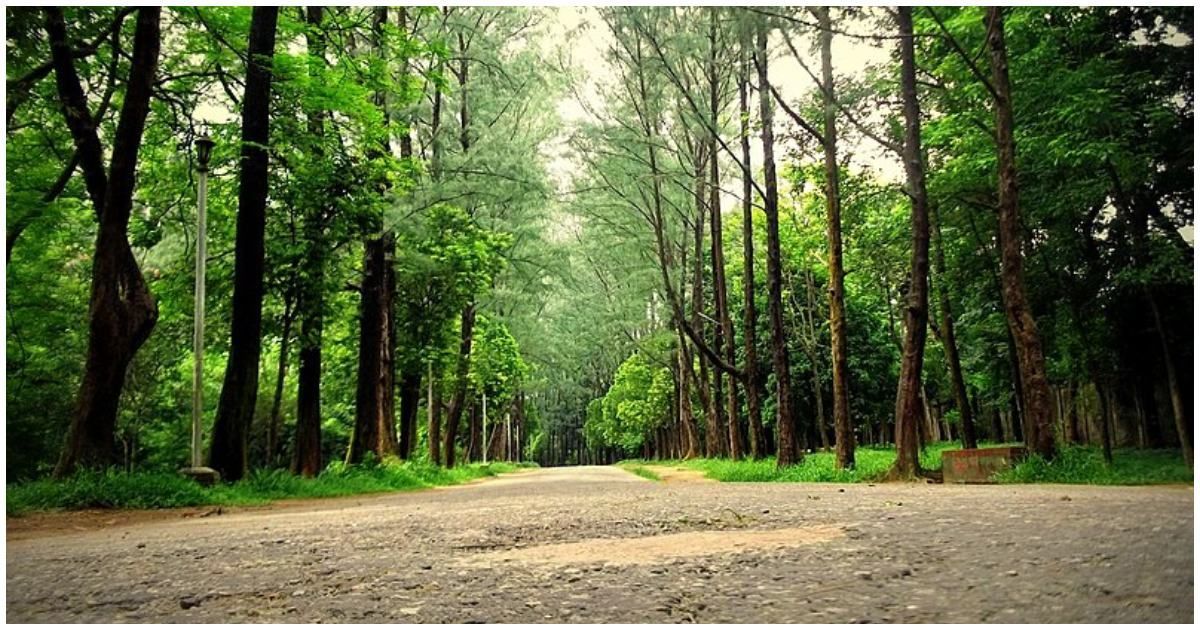





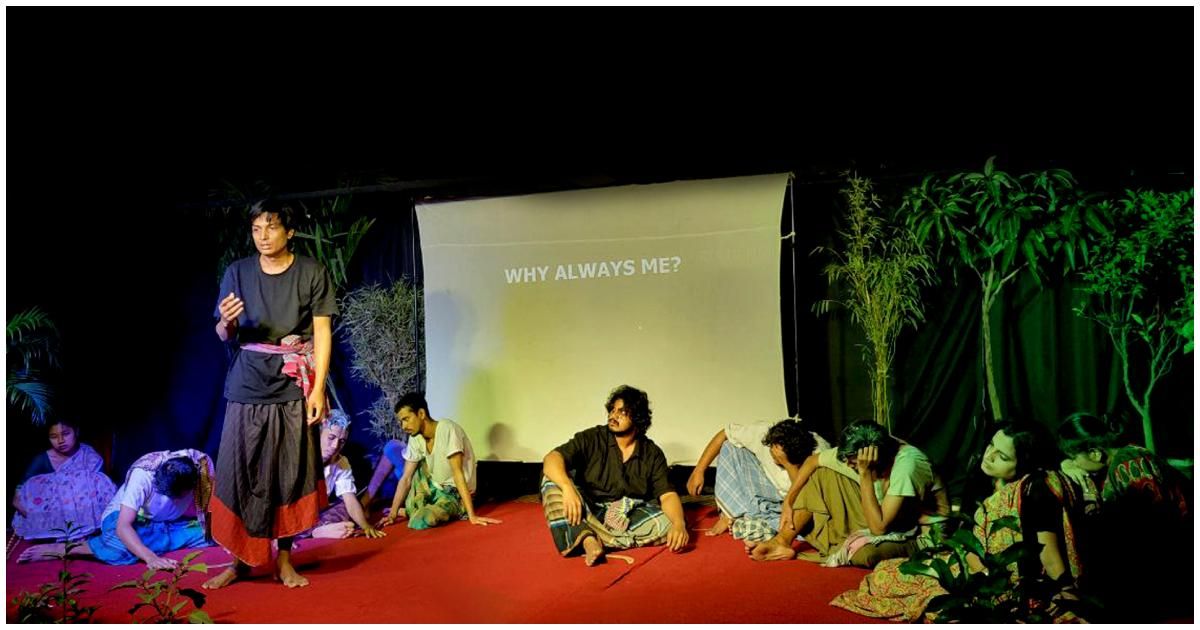
 ফাইল ছবি।
ফাইল ছবি।
মন্তব্য