বৃষ্টি মৌসুমগুলোতে ভারী বর্ষণের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে দেখা দেয় বন্যা। আর বন্যা মানেই নানা ধরণের কীট-পতঙ্গের পাশাপাশি শুরু হয় সাপের উপদ্রব। এমনকি এই চিত্র কেবল গ্রামেরই নয়, শহরাঞ্চলগুলোরও একই অবস্থা। এছাড়া যারা বর্ষার সময় বনে বা পাহাড়ে ঘুরতে যান তাদেরও প্রায় সময় সাপের কবলে পড়তে হয়। তাছাড়া বিগত বছরগুলোতে দেশ জুড়ে সাপে কাটার ঘটনা আশঙ্কাজনক মাত্রায় রয়েছে। সব থেকে উদ্বেগের ব্যাপার হলো- সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে অনেকেই পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হন। তাই চলুন, সাপে কামড়ালে কি করণীয় এবং কোন বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে হবে তা জেনে নেওয়া যাক।
সাপে কাটলে কি করা উচিত
সাপে কাটা ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। হাসপাতালে যাওয়ার পথে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত:
- সাপে কামড়ানো ব্যক্তি প্রায় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অনেক ক্ষেত্রে এই মানসিক অবস্থা প্রাণঘাতী হতে পারে। তাই আক্রান্ত ব্যক্তির ভয় দূর করে তাকে আশ্বস্ত করতে হবে এবং সাহস দিতে হবে। বিশেষত নির্বিষ সাপের দংশনে মৃত্যু হয় না। আর বাংলাদেশের অধিকাংশ সাপেরই বিষ নেই। বিষধর সাপের সংখ্যা খুবই কম। তাছাড়া এগুলো অধিকাংশ সময় শিকারের শরীরে পর্যাপ্ত বিষ ঢুকিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়।
- ব্যক্তির আক্রান্ত অঙ্গকে অবশ্যই স্থির করে রাখতে হবে। খুব বেশি নড়াচড়া করা যাবে না। হাঁটাচলা বা অধিক ঝাঁকুনির সম্মুখীন না করে স্থির ভাবে আধশোয়া অবস্থায় রাখা উত্তম।
- ক্ষতস্থানে একটু চাপ প্রয়োগ করে ব্যান্ডেজ বেধে দিতে হবে। এই প্রাথমিক চিকিৎসাটি প্রেসার ইমোবিলাইজেশন নামে পরিচিত। ব্যান্ডেজের বদলে গামছা, ওড়না বা এ জাতীয় কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে।
- রোগী শ্বাস না নিলে অবিলম্বে তার মুখে শ্বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- আক্রান্ত স্থান জীবাণুমুক্ত করার জন্য সাবান দিয়ে ধুয়ে ভেজা কাপড় দিয়ে হাল্কা ভাবে মুছে নিতে হবে।
পড়নে অলঙ্কার বা ঘড়ি কিংবা তাগা, তাবিজ থাকলে তা খুলে ফেলতে হবে। নতুনবা এগুলো রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, যা চিকিৎসা প্রক্রিয়ার জন্য ক্ষতিকর।
সাপে কামড়ালে যে ভুলগুলো করা উচিত নয়
- সাপে কাটা ব্যক্তিকে ওঝার কাছে নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।
- আক্রান্ত অঙ্গে কোনও ধরণের ভেষজ ওষুধ, উদ্ভিদের বীজ, লালা, গোবর, কাদা, বা পাথর লাগানো যাবে না।
- অনেকেই মনে করে থাকেন যে, আক্রান্ত স্থানে মুখ দিয়ে টেনে বিষ বের করলে রোগী ভালো হয়ে যায়। কিন্তু সাপের বিষ আসলে লসিকা ও রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়, যা এই পদ্ধতিতে বের করা অসম্ভব। এছাড়া আক্রান্ত স্থানে যিনি মুখ দিচ্ছেন, তার জন্যও বিষয়টি ক্ষতিকর।
- কামড়ানোর স্থানে অনেকে শক্ত বাঁধন বা গিট দিয়ে বাঁধেন। কিন্তু এমনটি একদমি উচিত নয়। বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে কামড়ানোর স্থান থেকে কিছুটা ওপরের দিকে শক্ত করে বাঁধা হয়। মূলত এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এতে বরং উল্টো রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে সঠিক রক্ত প্রবাহের অভাবে টিস্যুতে পচন বা নেক্রোসিস-এর উপক্রম হতে পারে।
- দংশনের স্থানে ছুরি বা ব্লেড দিয়ে আঁচড় দেওয়া যাবে না। বিষ বের করার জন্য অনেকে এমনটি করেন। কিন্তু এর জন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞের সরণাপন্ন হওয়া উচিত।
- ব্যথা দূর করতে মোটেই অ্যাস্পিরিন জাতীয় ওষুধ খাওয়ানো যাবে না।
- কোনও ধরণের রাসায়নিক পদার্থ লাগানো বা তা দিয়ে আক্রান্ত স্থানে সেঁক দেওয়া ঠিক নয়।
- অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তির খাবার বা ঢোক গিলতে কিংবা কথা বলতে সমস্যা হয়। পাশাপাশি নাসিক কণ্ঠস্বর, বমি, বা অতিরিক্ত লালা নিঃসরণের মত ঘটনা ঘটে। এগুলোর প্রতিকার হিসেবে তাকে কিছু খাইয়ে বমি করানোর চেষ্টা করা হয়। এই কাজটি একদমি অনুচিত।
শেষাংশ
সাপে কাটা ব্যক্তিকে বাঁচাতে তাৎক্ষণিকভাবে এই করণীয়গুলো যথেষ্ট কার্যকর। সাপের বিষ বের করার বা দংশনের ব্যথা উপশমে বিভিন্ন ভুল ধারণাগুলো সমাজে প্রচলিত রয়েছে। এগুলো পরিহার করে ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে আক্রান্ত অঙ্গ নাড়াচাড়া না করা এবং অতিরিক্ত চাপ প্রশমনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। সেই সাথে দংশিত স্থান জীবাণুমুক্ত করা একটি উৎকৃষ্ট উপায়। সর্বপরি, চিকিৎসা সংক্রান্ত এই প্রাথমিক জ্ঞান যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার আত্মবিঃশ্বাস যোগায়।

 রহমান মাসুদ
রহমান মাসুদ




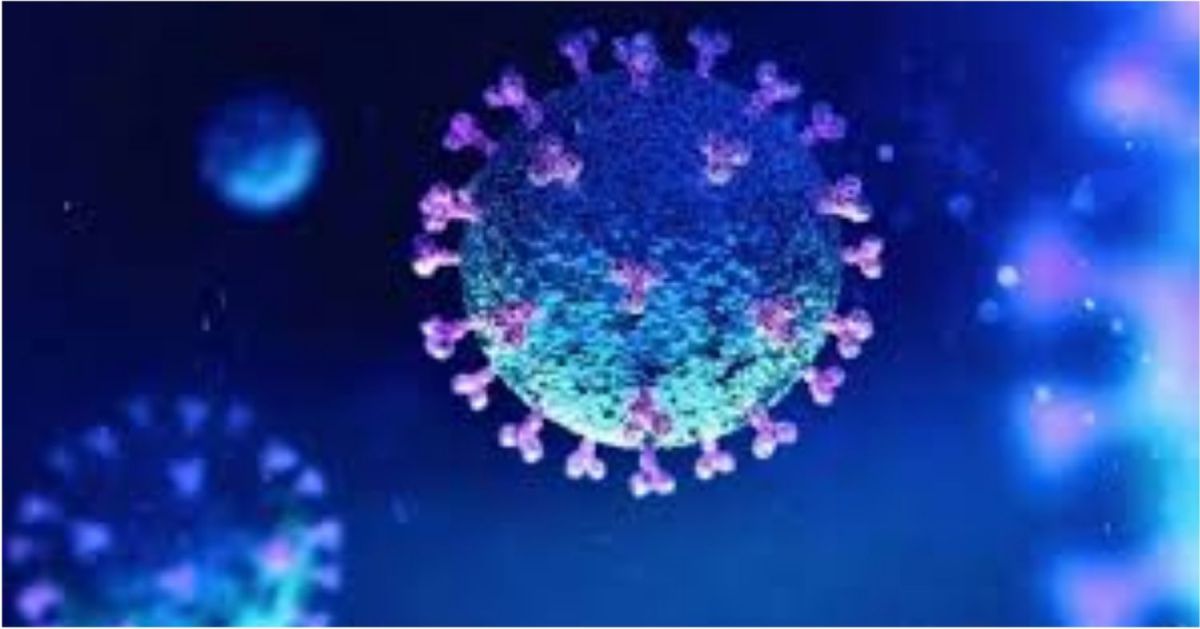
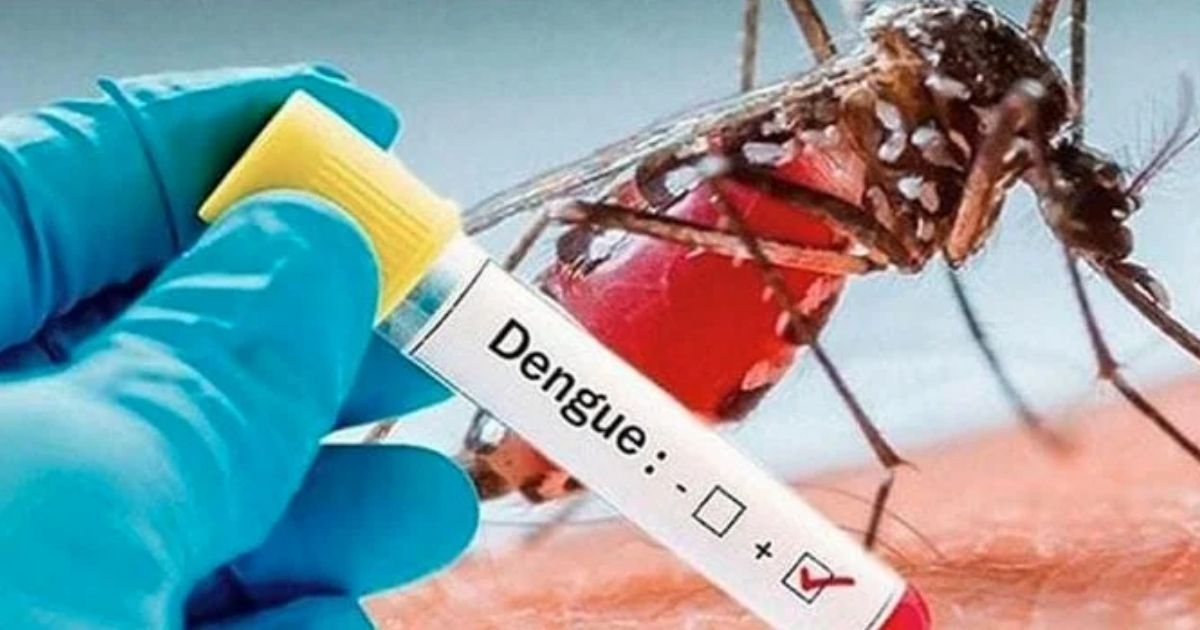



 স্বপ্ন নিয়ের উদ্যোগে গত ২০ মার্চ ঢাকার শ্যামলীতে অবস্থিত কৃত্রিম পা, হাত ও ব্রেইস সংযোজন কেন্দ্র ইজি লাইফ ফর বাংলাদেশে ১০ জনের কৃত্রিম পা সংযোজনের কার্মক্রম শুরু হয়। ছবি: স্বপ্ন নিয়ে
স্বপ্ন নিয়ের উদ্যোগে গত ২০ মার্চ ঢাকার শ্যামলীতে অবস্থিত কৃত্রিম পা, হাত ও ব্রেইস সংযোজন কেন্দ্র ইজি লাইফ ফর বাংলাদেশে ১০ জনের কৃত্রিম পা সংযোজনের কার্মক্রম শুরু হয়। ছবি: স্বপ্ন নিয়ে
মন্তব্য