দেশে নিত্যপণ্যের বাজার পরিস্থিতি বুঝতে এখন কারও সশরীরে বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আশপাশে সরকারি বিপণন প্রতিষ্ঠান ট্রেডিং করপোরেশন অফ বাংলাদেশের (টিসিবি) ভর্তুকি দামে খোলা ট্রাকে পণ্য বিক্রির তৎপরতাই বাজারের প্রকৃত চিত্র সবার কাছে স্পষ্ট করে দেয়।
টিসিবির এমন কার্যক্রম সারা বছর চলে না। বাজারে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি হলেই কেবল সক্রিয় হয় এ সংস্থাটি। তখন ছোট্ট পরিসরে তিন-চারটি পণ্য নিয়ে অল্প কয়েক দিনের জন্য মাঠে তাদের তৎপরতা চলে।
তবে বাজারে টিসিবির ভূমিকা সব সময় এত নাজুক ছিল না। একটা সময় বাজার নিয়ন্ত্রণ করত টিসিবিই। ব্যবসাও হতো তাতে। লক্ষ্য ছিল নির্দিষ্ট কিছু নিত্যপণ্যের আপৎকালীন মজুত গড়ে তুলে প্রয়োজনের সময় ভোক্তার কাছে তা সরবরাহ করার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা। সেই কার্যক্রমের আওতায় ভোক্তার তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাতে প্রচুর পণ্য আমদানি এবং সেগুলো ভোক্তাপর্যায়ে ন্যায্য দামে বিক্রির পাশাপাশি স্থানীয় অনেক ক্ষুদ্র শিল্পের জন্যও সংস্থাটি প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জোগান দিত।
তবে সময়ের পালাবদলে টিসিবির আগের জোরদার ভূমিকায় বিরাট ছেদ পড়েছে। বাজারে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে এটি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

কেন এটা ঘটেছে, জানতে চাইলে দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্টরা জানান, নব্বই দশকে দেশ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করার পর সরকার ব্যবসা করা ছেড়ে দিয়েছে। এতে বাজারে টিসিবির ভূমিকাও ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এসেছে। বাজারে সেই জায়গা দখল নিয়েছে ব্যবসায়ীরা।
অভ্যন্তরীণ ভোক্তার চাহিদাযোগ্য বিভিন্ন ভোগ্য ও ব্যবহার্য্য পণ্যের উৎপাদন, আমদানি, মূল্য সংযোজন, পরিশোধন এবং বাজারজাতকরণ– সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে তারা।
এর বিপরীতে কম মূলধন ও জনবল, অবকাঠামো দুর্বলতা, তিন-চারটি পণ্য এবং নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা নিয়ে কোনো মতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে টিসিবি।
টিসিবির পরিধি ছোট হয়ে আসায় দেশে ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে। এ কারণে মাঝেমধ্যেই বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। পণ্যের মজুত চলে যাচ্ছে বিভিন্ন স্তরে ব্যবসায়ীদের পকেটে। নানা কারসাজিতে সরবরাহ চেইন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন অজুহাতে বেড়ে যাচ্ছে পণ্যের দাম। এভাবে পণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতি চলতে থাকায় আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের হিসাব মেলানো কঠিন হয়ে পড়ছে স্বল্প ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের।
এ পরিস্থিতিতে টিসিবির খোলা ট্রাকের সামনে দীর্ঘ লাইনে মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যদেরও দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে।

কেন অস্থির হয় বাজার
দেশে সব নিত্যপণ্যের স্থানীয় উৎপাদন হয় না। কিছু পণ্যের উৎপাদন হলেও তা দিয়ে চাহিদা মেটে না। ফলে উৎপাদন হয় না কিংবা কম উৎপাদন হয়- এমন সব পণ্য আমদানির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ভোক্তার চাহিদা পূরণ করা হয়। এদিকে আমদানি বাজার সব সময় আবর্তিত হতে থাকে অস্থিরতার মধ্য দিয়ে। কখনও কমে, কখনও বাড়ে। ক্ষেত্রভেদে সকাল-বিকেলেও এই উত্থান-পতন দেখা যায়। এরই প্রভাব পড়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানিকারক দেশগুলোতে।
দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোজ্য তেল, চিনি, মসুর ডাল, ছোলা, পেঁয়াজ, খেঁজুরসহ বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ৬০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি করতে হয়। যার আমদানিকারক আবার গুটিকয়েক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। কিছু পণ্যের পরিশোধন কোম্পানির সংখ্যাও নগণ্য। এর বিপরীতে এসব নিত্যপণ্যের সরবরাহ ও বাজারজাতকরণে পরিবেশক, পাইকার ও খুচরা বিভিন্ন স্তরে ব্যবসায়ীর সংখ্যা লাখ লাখ। ফলে কোনো পণ্যের সরবরাহে ঘাটতি কিংবা দাম বেড়ে গেলে কোন স্তরে সমস্যাটি তৈরি হয়েছে তা তাৎক্ষণিক জানার উপায় কম।
বাজার অস্থিরতার নেপথ্যে কারা
নিত্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতা শুরু হলে কেউ দায় স্বীকার করতে চায় না। তদন্তের আগে সরকারের কাছেও তাৎক্ষণিক কোনো তথ্য থাকে না। এই সুযোগে চলতে থাকে একে অপরের ওপর দোষ চাপানো।
দেশে বছরের পর বছর নিত্যপণ্যের বাজার অস্থিরতার পেছনে কখনও আমদানিকারক, কখনও পরিশোধন ও বাজারজাতকারী কোম্পানিগুলোর সংঘবদ্ধ অপতৎপরতা দায়ী বলে চিহ্নিত হয়েছে। কখনও আবার চিহ্নিত হয়েছে পরিবেশক, পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সরাসরি দায়। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাজার সম্পর্কিত সব কটি গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ কারসাজিও চিহ্নিত হয়েছে।
কারা দায়ী, সরকার তা বুঝতে পারা এবং হস্তক্ষেপের আগেই ভোক্তার পকেট থেকে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা। উদ্বিগ্ন হওয়ার বিষয় হলো, সরবরাহ চেইনে আরও বড় ধরনের বিপর্যয় তৈরি হওয়ার আশঙ্কায় দায়ীদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারছে না। আবার বিপুল বিনিয়োগের প্রশ্ন জড়িত থাকায় গুটিকয়েক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধে বাজারে প্রতিযোগিতার ভারসাম্যও তৈরি করা যাচ্ছে না। এখানে মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণেও সরকারকে অনেক ক্ষেত্রে আপোষ করতে হচ্ছে।

দায়ী টিসিবির দুর্বল ভূমিকা
বাজারে কখনও সুনির্দিষ্ট কোনো পণ্যের, আবার কখনও একযোগে বিভিন্ন নিত্যপণ্যের স্বাভাবিক সরবরাহে ঘাটতি তৈরি হয়। এ ঘাটতির পেছনে বাস্তব পরিস্থিতির চেয়ে কারসাজির ভূমিকাই বেশি থাকে। এতে সংশ্লিষ্ট পণ্যের দামও বেড়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।
বাজার বিশ্লেষকরা এমন পরিস্থিতিতে টিসিবির প্রয়োজনকে গুরুত্বের সঙ্গেই দেখছেন। ১৭ কোটি ভোক্তার এই দেশে সংস্থাটির বিদ্যমান কার্যক্রম যথেষ্ট বলে মনে করছেন না তারা।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই বিরাট জনগোষ্ঠীর বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে টিসিবির যে সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন, সেটি আসলে নেই। সংস্থাটির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম চলে শুধু স্বল্প আয়ের মুষ্টিমেয় লোকের জন্য। সেটিও বছরব্যাপী নয়। বিক্রীত পণ্যের সংখ্যাও কম। আবার যা সরবরাহ দেয়া হয়, তাও সীমিত; রাজধানীসহ মাত্র ১২টি অঞ্চলের শুধু শহরকেন্দ্রিক এলাকাগুলোতে।
সারা দেশে বেশির ভাগ এলাকা টিসিবির কাভারেজের বাইরে থেকে যাচ্ছে। আবার টিসিবি থেকে পণ্য কেনার পরও সংশ্লিষ্ট ভোক্তাকে অন্যান্য নিত্যপণ্যের জন্য নিয়মিত বাজারেরই মুখাপেক্ষি হতে হচ্ছে।
এ বিষয়ে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের (ক্যাব) ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম নাজের হোসেন বলেন, ‘এবার রমজানে ব্যতিক্রম ছাড়া বছরব্যাপী টিসিবির কাভারেজ এরিয়া বলতে গেলে খুবই কম। তা সত্ত্বেও বাজার দামের এই ঊর্ধ্বগতিতে স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে টিসিবিই এখন ভরসা হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই পণ্য কেনায় মানুষের চাপ যে হারে বাড়ছে, সে অনুযায়ী টিসিবি তো তা সরবরাহ দিতে পারছে না। ভোক্তারা তো শুধু তিন-চারটি পণ্যই কেনেন না, তারা আরও অনেক পণ্য কেনেন।
‘আবার যে পরিমাণ পণ্য দেয়া হয়, তা দিয়ে বেশির ভাগ পরিবারের চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। সব মিলিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে টিসিবির ভূমিকা খুবই দুর্বল। সব দিক থেকে টিসিবির সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি।’
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আমদানি) এ এইচ এম সফিকুজ্জামান অবশ্য টিসিবির কার্যক্রমের প্রভাব কমে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করতে রাজি নন। তিনি বলেন, ‘অংশগ্রহণ কম হলেও বাজার নিয়ন্ত্রণে এখনও টিসিবি কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। বছরে বিভিন্ন সময় পরিচালিত টিসিবির স্বল্প পরিসরের এই অংশগ্রহণও যদি না থাকত, তাহলে নানামুখী ছাড় দিয়েও বাজার নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়ত। টিসিবি কাজ করছে বলেই ঊর্ধ্বগতির বাজার পুনরায় স্থিতিশীলতায় ফিরে আসছে। কারসাজি বা সিন্ডিকেট কোনোটাই সুবিধা করতে পারছে না।’
বাজার চাহিদার কতটুকু টিসিবি সরবরাহ করে
বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি নিউজবাংলাকে বলেন, ‘বাজার চাহিদা সব সময় এক রকম থাকে না। সারা বছর যে চাহিদা থাকে, রমজানে পণ্যভেদে তার দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়। এবার রমজানে টিসিবি সরবরাহকৃত প্রতিটি পণ্য বাজার চাহিদার ৩০ শতাংশ পর্যন্ত পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে।’
টিসিবির মুখপাত্র হুমায়ূন কবির ভূইয়া জানান, একটা সময় পণ্যভেদে বাজারে টিসিবির অংশগ্রহণ মাত্র ১ থেকে ৩ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে টিসিবি বছরজুড়ে পরিচালিত কার্যক্রমে প্রতিটি পণ্যের বাজার চাহিদার ১০-১২ শতাংশ পর্যন্ত সরবরাহ দিতে সক্ষম হচ্ছে।’
সরকারের উপলব্ধি
দেরিতে হলেও টিসিবির কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে সরকার। তাই শুধু এক মাসের (রমজান) জন্য হলেও টিসিবির পণ্য বিক্রির পরিধি সারা দেশে বিস্তৃত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ১ কোটি পরিবারকে এর উপকারভোগীর আওতায় আনা হয়েছে।
বাজারে পণ্যের দামের ধারাবাহিক উত্তাপ থেকে স্বল্প আয়ের মানুষ, দরিদ্র্য ও অতিদরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি নিউজবাংলাকে জানান, ‘ভবিষ্যতে টিসিবিকে আমরা ভেরি স্ট্রং পজিশনে রাখতে চাই। আমরা সে লক্ষ্যেই কাজ করছি। প্রধানমন্ত্রী চান টিসিবিকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে, যাতে যখনই প্রয়োজন পড়বে, টিসিবি যেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই রমজানে টিসিবির শক্তির পরীক্ষা হয়েছে। ১ কোটি পরিবারের কাছে মাত্র এক-দেড় মাসের মধ্যে পণ্য পৌঁছে দেয়ার কাজটি সহজ ছিল না। কিন্তু সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও টিসিবি সেটি করে দেখিয়েছে। এর মাধ্যমে টিসিবি যে শক্তি সঞ্চয় করেছে, ভবিষ্যতে প্রতিটি পদক্ষেপে তার সক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। টিসিবি সক্রিয় থাকলে বাজারে অনেক অঘটনও প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।’
বর্তমানে বছরব্যাপী বিভিন্ন সময় দেশের ১২টি অঞ্চলে টিসিবির পণ্য বিক্রি হয়ে থাকে, যা নিয়ন্ত্রণ করা হয় ঢাকার কাওয়ানবাজারের প্রধান কার্যালয় থেকে। এর বাইরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, ময়নসিংহ এবং মৌলভীবাজার আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। এ ছাড়া ক্যাম্প অফিস রয়েছে কুমিল্লা, মাদারীপুর, ঝিনাইদহ ও বগুড়ায় রয়েছে।
টিসিবির সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এটির কার্যক্রমকে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী করে ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন।
সম্প্রতি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি জানান, মাঠ পর্যায়ে টিসিবির পণ্য বিক্রি সবসময় প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজনগুলো সারা বছর থাকেও না। মাঝে মাঝে টিসিবির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। তখন সেটার ব্যবস্থা টিসিবিকে করতে হয়। তাই এখন থেকে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে টিসিবিকে পূর্ণ মাত্রায় সহযোগিতা করবে সরকার। এর জন্য যখন যা করার প্রয়োজন পড়বে, তখনই টিসিবির জন্য তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
অর্থমন্ত্রী বলেন, ‘টিসিবি বাজারে প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা অর্জন করলে সিন্ডিকেটের অস্তিত্ব থাকবে না। এর ফলে বাজারে মালামাল থাকার পরেও যারা অধিক মুনাফার আশায় সিন্ডিকেট করে, তাদের সেই সুযোগ বন্ধ হবে।’
টিসিবির যতো প্রতিবন্ধকতা
প্রতিবেশী ভারতে দ্য স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (এসটিসি) ও ট্রেডিং করপোরেশন অব পাকিস্তান (টিসিপি) তাদের অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি বছরে হাজার কোটি টাকা মুনাফা করে। বিপরীতে টিসিবি ধুঁকছে অস্তিত্ব সংকটে।
বিভিন্ন সময় পরিচালিত টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রমে বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে সাতটি সমস্যায় ভুগছে টিসিবি। এগুলো হলো: প্রয়োজনীয় পণ্য কেনায় মূলধনের সংকট, ভোক্তাপর্যায়ে পৌঁছাতে পর্যাপ্ত জনবল ও দাপ্তরিক কার্যালয়ের অভাব, কেনা পণ্য মজুতে অবকাঠামো দুর্বলতা, স্বতন্ত্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হয়েও পরিস্থিতি বুঝে তাৎক্ষণিক পণ্য ক্রয়-বিপণনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা না থাকা, টিসিবির কেনাকাটা অগ্রিম আয়কর ও ভ্যাটমুক্ত না হওয়া, ভর্তুকি বরাদ্দ কম হওয়া, কার্যক্রম পরিচালনায় দুর্নীতি।
সংশ্লিষ্টরা জানান, এসব সমস্যা সমাধানে বারবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু এর কোনোটিই আশানুরূপ বাস্তবায়ন হয়নি। যে কারণে বাজার নিয়ন্ত্রণে টিসিবি ক্রমেই গুরুত্ব হারাতে বসেছে।
এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে টিসিবির সচিব (যুগ্ম সচিব) মো. মনজুর আলম প্রধান নিউজবাংলাকে জানান, ‘টিসিবিকে শক্তিশালী করতে জনবল, মাঠপর্যায়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম, আধুনিক গুদাম নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় অর্থ ও কেনাকাটায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানোর প্রক্রিয়াগুলো সব সময় চলমান। তবে একদিনে তো হওয়ার কথা নয়, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।
‘তবে এটা বলতে পারি, সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের কারণে ধীরে ধীরে টিসিবি আরও শক্তিশালী হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সংস্থার কার্যক্রমেরও সম্প্রসারণ ঘটছে। চলতি বছর সারা দেশে রাজধানী থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়েও পৌঁছে গেছে টিসিবির কার্যক্রম। ভবিষ্যতে বাজার নিয়ন্ত্রণে ইউনিয়ন পর্যায়েও টিসিবি সক্রিয় ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। সরকার সে লক্ষ্যেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।’
আরও পড়ুন:টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডে ভর্তুকি ৬৫৩ কোটি টাকা
সেই ৫ হাজার পরিবার পেল টিসিবির পণ্য
রাজনীতিতে ঝুলে আছে ৫০০০ কার্ড
টিসিবির পণ্যে আর্থিক লাভ, সময়ের ক্ষতি
টিসিবির কার্ডে ‘টাকা আদায়’, তদন্তে কমিটি
- ট্যাগ:
- টিসিবি

 শাহ আলম খান
শাহ আলম খান









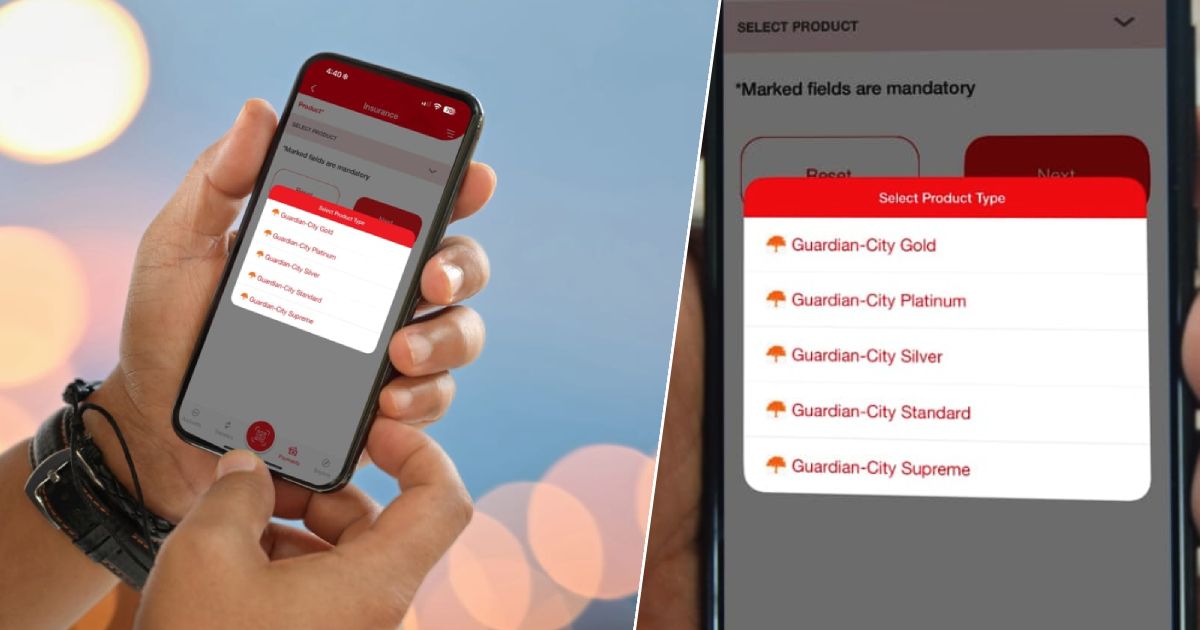
মন্তব্য