ফাইজার-বায়োএনটেক উদ্ভাবিত করোনাভাইরাসের টিকার জরুরি ব্যবহারের স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।
স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সংস্থাটি এ স্বীকৃতি দেয় বলে এএফপির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
৮ ডিসেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ফাইজার ও জার্মানির বায়োটেকনোলজি কোম্পানি বায়োএনটেক উদ্ভাবিত টিকা দেয়া শুরু করে যুক্তরাজ্য। পরে করোনার টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে।
ডব্লিউএইচওর পক্ষ থেকে বলা হয়, এক বছর আগে চীনে করোনা মহামারি শুরুর পর এই প্রথম ফাইজার-বায়োএনটেক উদ্ভাবিত টিকার স্বীকৃতি দেয়া হলো।
ইউনিসেফ, প্যান-আমেরিকান হেলথ অর্গানাইজেশনসহ অন্য সংস্থাগুলোকে করোনায় নাজুক পরিস্থিতিতে থাকা দেশগুলোতে টিকা সরবরাহের আহ্বান জানায় ডব্লিউএইচও।
ডব্লিউএইচওর শীর্ষ কর্মকর্তা ম্যারিয়েনগেলা সিমাউ বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে করোনার টিকা ব্যবহার নিশ্চিতে এটি বেশ ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে বিশ্বের সব প্রান্তে প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত টিকা সরবরাহে আরও বেশি বৈশ্বিক উদ্যোগে জোর দিতে চাই আমি।’
এর আগে নিজেদের ও বিশ্বের অন্য বিশেষজ্ঞদের ফাইজার-বায়োএনটেকের টিকার কার্যকারিতা ও গুণমান নিয়ে তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনার আহ্বান জানায় ডব্লিউএইচও।
পর্যালোচনায় টিকার নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা সংক্রান্ত ডব্লিউএইচওর মানদণ্ড ফাইজার-বায়োএনটেকের টিকা বজায় রেখেছে বলে ডব্লিউএইচও জানায়।
আরও ভয়াবহ মহামারির শঙ্কা: ডব্লিউএইচও
অনলাইনে মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন করবে ডব্লিউএইচও
- ট্যাগ:
- ডব্লিউএইচও





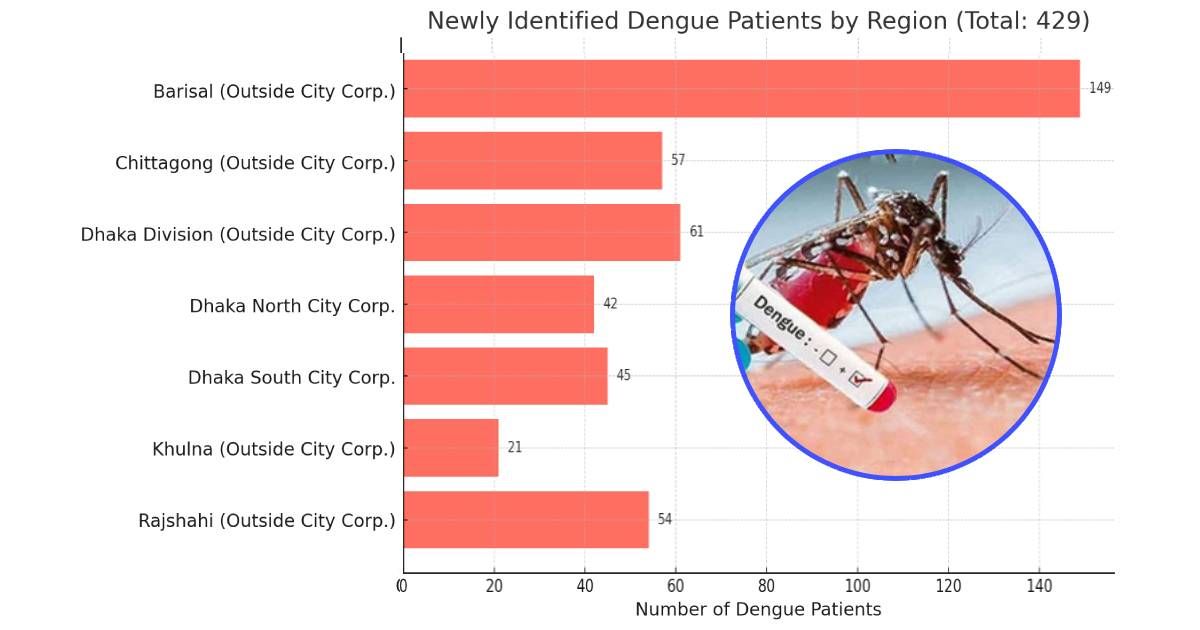
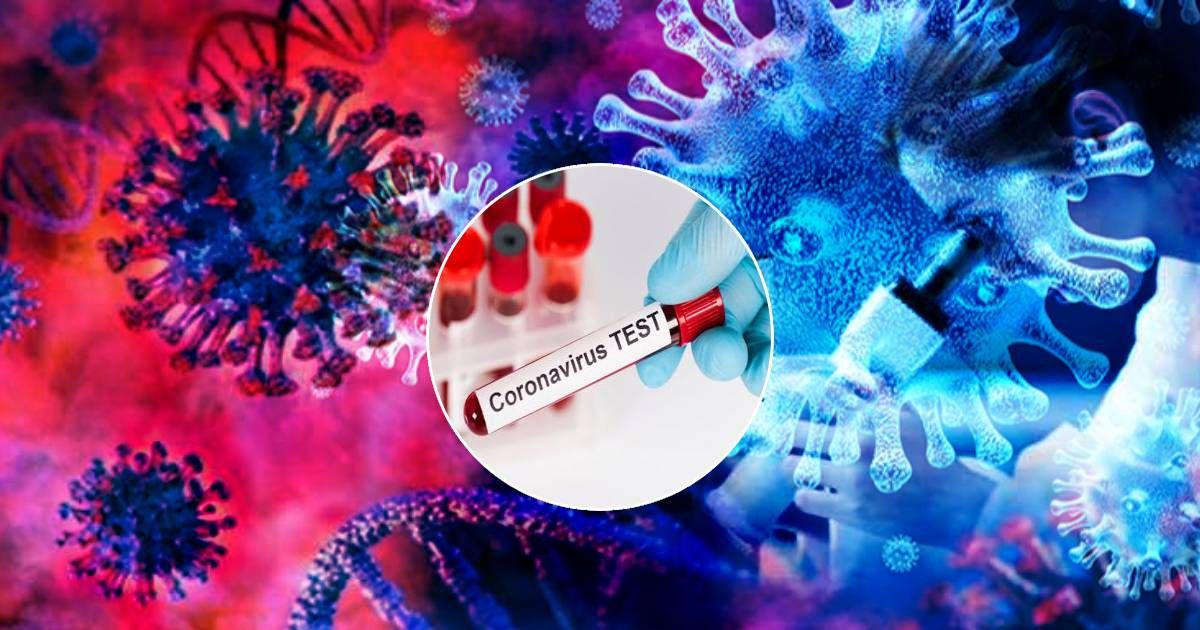





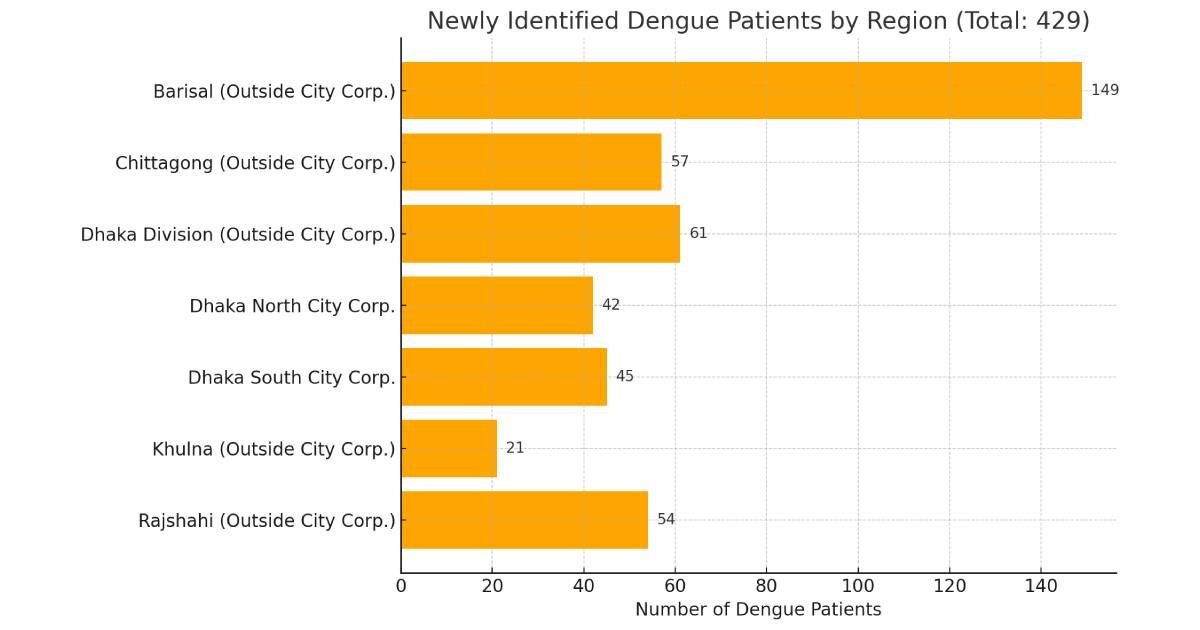

মন্তব্য