লিভারের মারাত্মক এক রোগ লিভার সিরোসিস। এ রোগে প্রতি বছরই অনেকের মৃত্যু হয়। প্রাণঘাতী রোগটির চিকিৎসা পদ্ধতি গত ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এক ভিডিওতে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হেপাটোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মেডিসিন, লিভার ও পরিপাকতন্ত্র রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ফরহাদ হোসেন মো. শাহেদ। পরামর্শগুলো তার ভাষায় পাঠকদের জন্য উপস্থাপন করা হলো।
লিভার সিরোসিসের চিকিৎসাটা আমরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকি। একটা হলো সাধারণ চিকিৎসা, একটা হলো যে সমস্ত কারণে লিভার সিরোসিস হয়, কারণভিত্তিক চিকিৎসা এবং সর্বশেষ হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন।
সাধারণ চিকিৎসা
সাধারণ চিকিৎসার মধ্যে আসবে রোগীর খাওয়া-দাওয়া। সাধারণত লিভার সিরোসিসের রোগীদের আমরা হাই প্রোটিন ডায়েট দিই, হাই ফাইবার ডায়েট দিই এবং ব্রাঞ্চড চেইন অ্যামাইনো অ্যাসিড দিই।
হাই প্রোটিন ডায়েটের মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এগুলো থাকবে। হাই ফাইবার ডায়েটের মধ্যে টাটকা শাকসবজি, ফলমূল এগুলো থাকবে। আর ব্রাঞ্চড চেইন অ্যামাইনো অ্যাসিডেরে মধ্যে মটরশুঁটি, মসুরের ডাল, বাদাম এগুলো থাকবে।
এ ধরনের খাবারগুলো দেওয়া হয়, কারণ লিভার সিরোসিস হচ্ছে একটা ক্ষয়জনিত রোগ। এখানে লিভার কাজ করে না। লিভার না কাজ করার কারণে রোগীরা শরীরে শক্তি পায় না। এভাবে আস্তে আস্তে ওয়েট (ওজন) কমে যায়। এ জন্য প্রোটিনটা খুবই ইম্পরট্যান্ট। প্রোটিন যাতে রোগীরা সঠিকভাবে পায়, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হয়।
লিভার সিরোসিস রোগীদের সাধারণ চিকিৎসার মধ্যে দুই নম্বর হলো সবসময় লিভার সিরোসিস রোগীদের কিছু না কিছু ইনফেকশন থাকে এবং অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া লাগে। তারপরে রোগীর বাথরুম যাতে ক্লিয়ার থাকে। গাট স্টেরিলাইজেশন। এ জন্য আমরা লেক্সেটিভজাতীয় কিছু দিয়ে থাকি, যেমন: অ্যাভোলাক সিরাপ, লেকটিটলের মতো ওষুধ দিয়ে থাকি, যাতে বাথরুম দুই থেকে তিনবার হয়। তাহলে রোগীর ইনফেকশনটাও কম হয়, গাট স্টেরিলাইজ থাকে। রোগীর ইমপ্রুভ থাকে।
এরপর হলো পোর্টাল হাইপারটেনশন থাকে। লিভার সিরোসিসের রোগীদের পোর্টাল প্রেশারটা কমায়া রাখতে হয়, যে কারণে আমরা ইনডেভারের মতো ওষুধগুলো প্রেসক্রাইব করে থাকি। পোর্টাল প্রেশার কম থাকলে ব্লিডিংয়ের সম্ভাবনাও কম থাকে। এগুলো হচ্ছে সাধারণ চিকিৎসা।
কারণজনিত চিকিৎসা
কারণের চিকিৎসার মধ্যে আছে, যাদের হেপাটাইটিস বি বা বি ভাইরাস থাকে, তাদের বি ভাইরাসের চিকিৎসা দেওয়া হয়। বি ভাইরাসের জন্য আগে ভাইরাস ধরা পড়লে আমরা এক বছর, দুই বছর, তিনি বছর পরীক্ষার মাধ্যমে যতটুকু ইন্ডিকেশন দিতাম, কিন্তু এখন যেটা গেছে ভাইরাসের চিকিৎসা বন্ধ করার পর অনেক রোগী আমাদের কাছে সিরোসিস বা ক্যানসার নিয়ে আসে।
কাজেই এখন ট্রেন্ড হচ্ছে ভাইরাসের ওষুধ বন্ধ করা যাবে না। ডাক্তারের পরামর্শমতো প্রয়োজনে ৪ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর যা লাগে, সবসময় কন্টিনিউ করতে হবে। লিভার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে যেভাবে খেলে ভালো হয়, সেভাবে খেতে হবে।
সি ভাইরাস যদি থাকে, আমরা সি ভাইরাসের চিকিৎসা দিয়ে থাকি। এটার একটা ভালো চিকিৎসা আছে।
ফ্যাটি লিভার যদি থাকে, অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে আমরা অ্যালকোহল বন্ধ করে দিই। আর নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারের কারণগুলোর মধ্যে হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, থাইরয়েড, ওবেসিটি এগুলো কমানোর কথা বলে থাকি।
এগুলো কমানোর সাথে সাথে এগুলো কন্ট্রোলের যে ওষুধ, সেগুলো আমরা খেতে বলি।
এরপর অটোইমিউন হেপাটাইটিস যদি থেকে থাকে, সেখানে আমরা স্টেরয়েড দিয়ে থাকি। এ ছাড়া যদি অটোইমিউন বিগ ডিজিজ থাকে, এগুলো চিকিৎসা করা হয়। এ ছাড়া উইলসন’স ডিজিজের মতো বংশগত যেসব রোগ আছে, এগুলোর সুন্দর চিকিৎসা আছে। চিকিৎসা করলে রোগী ইমপ্রুভ করে, অনেক দিন ভালো থাকে।
হার্ট ফেইলিউর রোগীদের যদি লিভার সিরোসিস থাকে, আমরা হার্ট ফেইলিউর কন্ট্রোল করি। তখন রোগী অনেক দিন ভালো থাকে।
ড্রাগসের কারণে যদি লিভার সিরোসিস হয়, সে অনুযায়ী ওষুধ পরিবর্তন করা হয়।
লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট
লিভার সিরোসিসের আমরা যে চিকিৎসাগুলো বলেছি, এগুলো এ কারণে যে, রোগী যেন জাস্ট সুস্থ থাকে এবং উপসর্গবিহীন থাকে, কিন্তু লিভার সিরোসিস যেটা হয়ে গেছে, এটার আসলে কোনো চিকিৎসা নাই। এর একটাই চিকিৎসা; লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট। এটা আমাদের দেশে চার-পাঁচটা অলরেডি হয়ে গেছে এবং সাকসেস খুবই ভালো। এ জন্য আমাদের বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি শিগগিরই লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট শুরু হচ্ছে। এটা নিয়ে এখন আর আমাদের কোনো চিন্তা নাই।
ইনশাল্লাহ যে সমস্ত লিভার সিরোসিস রোগী আছেন, আপনাদের চিকিৎসা ইনশাল্লাহ আছে। এটাও একটা চিকিৎসা, যেটাতে রোগী ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যায়, যে জন্য লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট এটা হচ্ছে লেটেস্ট ট্রিটমেন্ট। এটার মাধ্যমে রোগী সুস্থ হয়।
আরও পড়ুন:চোটে ছিটকে গেলেন লিভারপুল তারকা ভার্জিল ফন ডাইক
৮৫ বছর পর ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে হার লিভারপুলের
প্রতিপক্ষের জোড়া আত্মঘাতী গোলে জয় লিভারপুলের
কারাবাও কাপে লিভারপুলকে বিদায় করে কোয়ার্টারে ম্যানসিটি
লিভার নিয়ে যত কথা
- ট্যাগ:
- লিভার

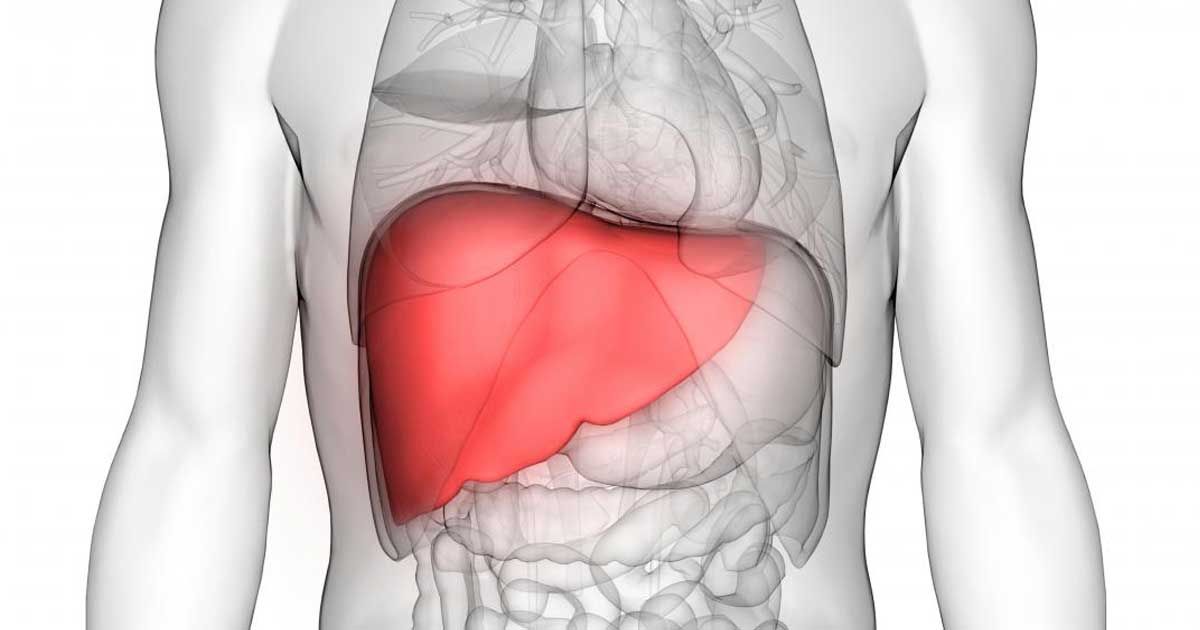


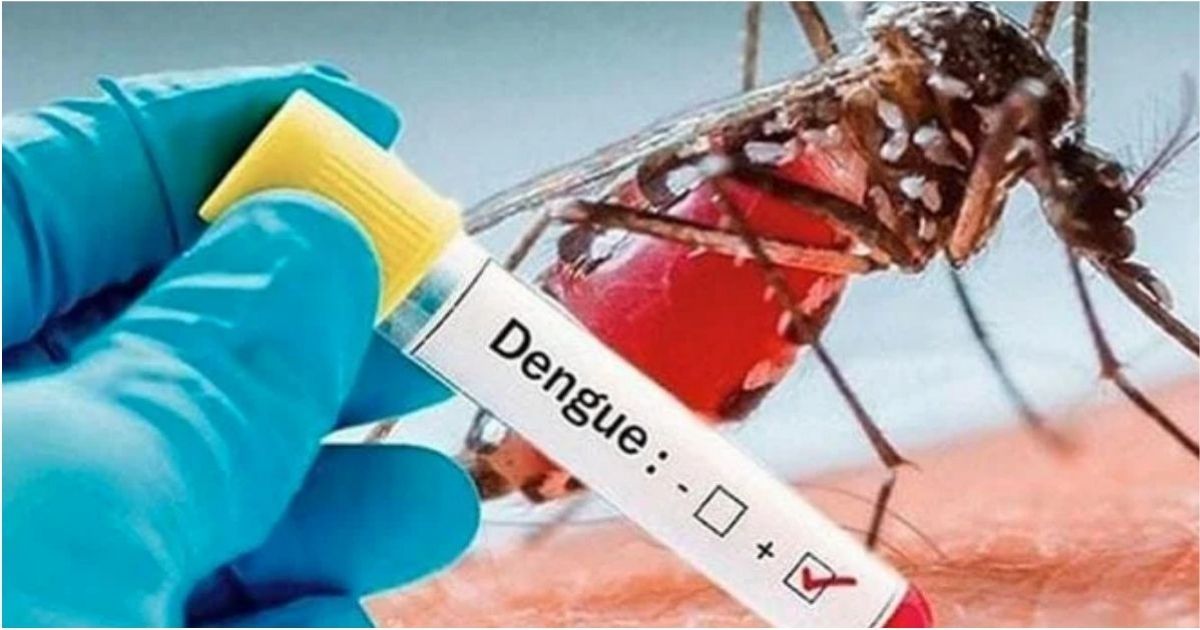







মন্তব্য