বিশ্বজুড়ে নানা ধরনের ক্যানসারে আক্রান্ত হন নারীরা। বিভিন্ন দেশে নারীরা সবচেয়ে বেশি যেসব ক্যানসারে আক্রান্ত হন, তার মধ্যে চতুর্থ সর্বোচ্চ স্থানে আছে জরায়ুমুখ ক্যানসার, বাংলাদেশে যেটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।
৯৯.৮ শতাংশের ক্ষেত্রে হিউম্যান প্যাপিলমা ভাইরাসের (এইচপিভি) সংক্রমণের ফলে রোগের সূচনা হয়। এ ক্যানসারের একটি পূর্বাবস্থা থাকে, যা ১৫ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। সাধারণত যৌন সঙ্গমের ফলে ভাইরাসটি দেহে অনুপ্রবেশ করে।
জরায়ুমুখ ক্যানসার ছাড়াও এইচপিভির মাধ্যমে যোনিদ্বার, যোনি, মুখগহ্বর, পিনাইল/পুরুষাঙ্গ ক্যানসার হয়ে থাকে।
আক্রান্তের ঝুঁকি বেশি কাদের
বাল্যবিবাহ, কম বয়সে সন্তান প্রসব, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, বেশিসংখ্যক সন্তান প্রসব কিংবা যৌন রোগ থাকলে জরায়ুমুখ ক্যানসার হতে পারে। নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে একাধিক যৌনসঙ্গী থাকলে এ রোগ হতে পারে।
এর বাইরে আর্থ-সামাজিক অবস্থা কিংবা স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে রোগটি হতে পারে।
জরায়ুমুখ ক্যানসার নির্মূলে বৈশ্বিক তৎপরতা
আগামী ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে জরায়ুমুখ ক্যানসার, গুটি বসন্ত ও পোলিওর মতো রোগ নির্মূল করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ২০১৯ সালের ১৭ নভেম্বরে ঘোষণা দেয়, জরায়ুমুখ ক্যানসার নির্মূল করতে ২০৩০ সালের মধ্যে কিছু লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।
সংস্থাটি জানায়, ৯০ শতাংশ কিশোরীকে এইচপিভি টিকা দিতে হবে। এ ছাড়া ২৫ থকে ৬০ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ৭০ শতাংশকে স্ক্রিনিং বা পরীক্ষার আওতায় আনতে হবে। এর বাইরে ক্যানসারপূর্ব অবস্থা বা জরায়ুমুখ ক্যানসার থাকা ৯০ শতাংশ নারীকে ২০৩০ সালের মধ্যে চিকিৎসা দেয়ার পাশাপাশি পেলিয়েটিভ কেয়ারের আওতায় আনতে হবে। এ ব্যবস্থাকে ডব্লিউএইচওর ৯০-৭০-৯০ ম্যানডেট বলা হচ্ছে।
ডব্লিউএইচওর মহাপরিচালক ডা. টেডরোস আধানম গেব্রিয়েসুস ২০১৮ সালের মে মাসে জরায়ুমুখ ক্যানসার নির্মূলে বৈশ্বিক তৎপরতার ডাক দেন। পরবর্তী সময়ে ২০২০ সালের আগস্টে এ ক্যানসার নির্মূলে বৈশ্বিক কর্মকৌশল গ্রহণ করে ডব্লিউএইচও। একই বছরের ১৭ নভেম্বর সে কর্মকৌশলের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশসহ ১৯৪টি দেশ এ কর্মকৌশলে নিজেদের সম্পৃক্ত করে।
বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়
জাতিসংঘের ২০২০ সালের ডেটা অনুযায়ী, আমাদের জনসংখ্যা ১৭ কোটি। উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমরা বর্তমানে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ২০২০ সালের ডেটা অনুযায়ী, আমাদের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ ডলার। এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে ২১.৮ শতাংশ মানুষ।
পৃথিবীর অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও জরায়ুমুখ ক্যানসারের প্রকোপ অনেক বেশি। গ্লোবকনের ২০২০ সালের ডেটা অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় ৮ হাজার ২৬৮ জন নারীর জরায়ুমুখ ক্যানসার শনাক্ত হয়। এ ক্যানসারে বার্ষিক মৃত্যু হয় ৪ হাজার ৯৭১ নারীর।
যেহেতু এখন পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো বেড়ে চলেছে এবং অপর্যাপ্ত পরীক্ষা হয়েছে, সেহেতু বাংলাদেশে স্তন ক্যানসারের পরই জরায়ুমুখ ক্যানসারে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে নারীরা।
২০০৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৪.৩ শতাংশ নারীর ভিজ্যুয়াল ইন্সপেকশন উইথ অ্যাসেটিক অ্যাসিড তথা ভিআইএ পদ্ধতির মাধ্যমে জরায়ুমুখ ক্যানসার পরীক্ষা করা হয়েছে।
২০১০ সালে বাংলাদেশে হাজারে মাতৃমৃত্যু ছিল ৩১০। ২০১৫ সালে সেটি কমে দেড়শতে নেমে আসে। সেদিক থেকে দেখলে জরায়ুমুখ ও অন্যান্য ক্যানসারজনিত রোগে মৃত্যুহার বেড়েছে।
আমাদের করণীয় কী
জরায়ুমুখ ক্যানসার নির্মূল ও আক্রান্তদের রক্ষায় আমাদের বেশ কিছু করণীয় আছে। সেগুলো এখন তুলে ধরছি।
১. আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এইচপিভি টিকাদান। এ নিয়ে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ সার্ভিক্যাল ক্যানসার ভ্যাকসিনেশন (জরায়ুমুখ ক্যানসার টিকাদান) কমিটি একটি পাইলট কর্মসূচি চালু করে। সে কর্মসূচির আওতায় ছিল ৬৭ জন মেয়ে, যাদের বয়স ৯ থেকে ১৫ বছর। তাদের মধ্যে ৫০ জনকে টিকা দেয়া হয়। ১৭ জন কন্ট্রোল হিসেবে থাকে। ৯৭.৫ শতাংশ মেয়ের সেরো কনভারশন হয়। ৭ বছর পর তাদের ৯৩.৩ শতাংশের দেহে অ্যান্টি এইচপিভি ১৬/১৮ অ্যান্টিবডি তৈরি হয়।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে গাজীপুরে আরেকটি পাইলট কর্মসূচি নেয়া হয়। ৬ মাসের ব্যবধানে দুটি টিকা দেয়া হয় ১০ বছর বয়সের মেয়েদের। সে কর্মসূচির প্রথম বছরে ৮৯ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বছরে ৯৮ শতাংশ মেয়েদের টিকা দেয়া হয়।
টিকাদানের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে।
(ক) ২০২২ সালের মধ্যে এইচপিভি টিকা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) আওতাভুক্ত করতে হবে।
(খ) বর্তমানে ৯০ শতাংশ টিকাদান কর্মসূচি হয় স্কুলভিত্তিক। স্কুলের বাইরে মেয়ের টিকা দিতে হবে। ছেলেদেরও টিকা দিতে হবে।
(গ) কিছু বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। যেমন: বাল্যবিয়ে না করা, একাধিক যৌনসঙ্গী না রাখা, অল্প বয়সে সন্তান ধারণ না করা, অল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার সন্তান প্রসব না করা, ধূমপান না করা, জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ৫ বছরের বেশি সময় গ্রহণ না করা, যৌনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।
১০ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের মধ্যে টার্গেট গ্রুপ হলো ৮ লাখ ৩১ হাজার।
২. জরায়ুমুখ ক্যানসার মোকাবিলায় দ্বিতীয় লক্ষ্য হবে ৭০ শতাংশ নারীকে স্ক্রিনিং বা পরীক্ষার আওতায় আনা। উন্নত দেশে পাপ্স স্মেয়ার প্রচলিত আছে। যথেষ্ট ল্যাবরেটরি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল না থাকায় বাংলাদেশে ভিআইএ বা ভায়া স্ক্রিনিং পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে স্ক্রিনিং শুরু করা হয়।
এ নিয়ে ২০০৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমউ) পাইলট প্রকল্প শুরু হয়। ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল নাগাদ ন্যাশনাল সেন্টার ফর ভায়া অ্যান্ড সিবিই সক্রিয় কার্যক্রম চালায়। ২০১৮-২১ মেয়াদে ‘ইলেকট্রনিক ডেটা ট্র্যাকিং উইথ পপুলেশন বেইজড সার্ভিক্যাল অ্যান্ড ব্রেস্ট ক্যানসার স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম’ নামের কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়।
বর্তমানে দেশে ভিআইএ কেন্দ্র আছে ৫০০টি। এ মুহূর্তে ভিআইএ সম্পৃক্তদের মধ্যে ২ হাজার ৩৮৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাদের মধ্যে ৪০০ চিকিৎসক, ১ হাজার ৯৫৬ নার্স, এফডব্লিউভি ও প্যারামেডিকস রয়েছেন।
দেশে ৭ কোটি ৫ লাখ নারীর মধ্যে টার্গেট গ্রুপ হলো ৩ কোটি। ২০১৯ সাল পর্যন্ত ভিআইএ পদ্ধতির মাধ্যমে ১০ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ১৪.৩ শতাংশের পরীক্ষা হয়েছে। এ সময়ে পরীক্ষা করা হয়েছে ২৪ লাখ ৪৭১ জনকে। তাদের মধ্যে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ বা ১ লাখ ৮ হাজার ৩২৬ জনের ফল পজিটিভ এসেছে।
স্ক্রিনিংয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু করণীয় রয়েছে। সেগুলো নিচে উল্লেখ করছি।
(ক) দেশের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, ৮৬ শতাংশ নারীর স্ক্রিনিং হয়নি। এ কারণে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে হবে। অর্থাৎ ভিআইএর সঙ্গে প্রাথমিক স্ক্রিনিং টেস্ট হিসেবে এইচপিভি ডিএনএ টেস্টের প্রবর্তন করতে হবে।
(খ) পলিসি প্রবর্তন গাইডলাইন তৈরি করতে হবে।
(গ) ন্যাশনাল স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম বা জাতীয় পরীক্ষা কর্মসূচির আওতায় ৩০ থেকে ৬০ বছর বয়সী নারীদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে নিতে হবে।
(ঘ) ডব্লিউএইচওর মতে, একজন নারীর জীবনে দুবার পরীক্ষা করালে আর জরায়ুমুখ ক্যানসারের প্রয়োজন হয় না। দুবার পরীক্ষার মধ্যে কমপক্ষে ৫ বছর বিরতি দিতে হবে। সে বিষয়টি মাথায় রেখে কর্মসূচি সাজাতে হবে।
(ঙ) হাসপাতালভিত্তিক পরীক্ষার পরিবর্তে জনসংখ্যাভিত্তিক পরীক্ষা হতে হবে। এ ক্ষেত্রে টার্গেট জনসংখ্যা হবে ৩ কোটি।
এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন: ‘সি অ্যান্ড ট্রিট’ নামে কুড়িগ্রামে একটি পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়। ২০১৯ সালের প্রথম সপ্তাহে চালু হওয়া এ প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৩ সাল পর্যন্ত।
এ প্রকল্পের আওতায় ভিআইএ-মিনি কলপোস্কোপি-থার্মোকোয়াগুলেশন পদ্ধতিতে টার্গেট জনসংখ্যা ধরা হয় ৬০ হাজার। এর মধ্যে কাভারেজে এসেছে ৩০ হাজার ৭৫২ বা ৫০ শতাংশ।
কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমেও জরায়ুমুখ ক্যানসার পরীক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রতি কমিউনিটি ক্লিনিকে ৬০০ থেকে ৭০০ নারীকে পরীক্ষা করা হবে। মোট ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে ৯১ লাখ নারীর স্ক্রিনিং সম্ভব হবে।
৩. জরায়ুমুখ ক্যানসার নির্মূল পরীক্ষার লক্ষ্য নিশ্চিতের পাশাপাশি আরেকটি দিক মাথায় রাখতে হবে। সেটি হলো পরীক্ষার বিষয়টি বাস্তবায়ন কারা করবে। এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয় নজরে আনতে হবে।
(ক) বিভাগীয় পর্যায়ে ৮টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ক্যানসার সেন্টার এবং অন্যান্য সেন্টারে জরায়ুমুখ ক্যানসার পরীক্ষা করাতে হবে। ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী নারীদের এর আওতায় আনতে হবে।
(খ) চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এইচপিভি জিনোটাইপের জন্য পিসিআর ল্যাব প্রস্তুত করতে হবে।
(গ) সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও ৮টি বিভাগীয় ক্যানসার সেন্টারে পিসিআর ল্যাব তৈরি করতে হবে।
(ঘ) লক্ষ্য অর্জনে বর্তমানে উন্নয়নশীল ১০টি দেশ প্রাইমারি স্ক্রিনিং হিসেবে ভিআইএর পরিবর্তে এইচপিভি ডিএনএ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করছে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ঢাকায় ৬৮টি পিসিআর ল্যাব, অন্যান্য শহরে ৫০টি পিসিআর ল্যাবসহ ১১০টি ল্যাবকে এইচপিভি জিনোটাইপিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে বিএসএমএমইউ, জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং ওজিএসবি হাসপাতালে এ ধরনের ল্যাব আছে।
(ঙ) নারীরা যেন নিজেরাই সোয়াবের মাধ্যমে স্যাম্পল নিতে পারেন, সে জন্য ভিডিও প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।
(চ) শিক্ষার্থী, সমাজকর্মী, ক্যানসার সারভাইভার, সেবাদানকারী মিলে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।
৪. জরায়ুমুখ ক্যানসার নির্মূলে তৃতীয় লক্ষ্য হলো ক্যানসারপূর্ব অবস্থায় থাকা এবং শনাক্ত হওয়া ৯০ শতাংশ নারীকে চিকিৎসা দেয়া।
বিএসএমএমইউয়ের গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজি বিভাগ, এনআইসিআরএইচ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে এ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
প্রতিটি জরায়ুমুখ ক্যানসারজনিত মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ এই ক্যানসার প্রতিরোধ করা সম্ভব। বর্তমানে বছরে ৪ লাখ নারীর স্ক্রিনিং হচ্ছে। কাজেই ৭০ শতাংশ নারীকে স্ক্রিনিংয়ের আওতায় আনা খুব কঠিন হবে।
২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদের আরও পর্যালোচনা দরকার।
পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়া নারীদের দুইভাবে চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে। ডব্লিউএইচওর মতে, আলাদাভাবে ট্রেয়াজের মাধ্যমে একত্রিত করা। এ ক্ষেত্রে ভিআইএর আওতাধীন কলপোস্কপি/সিটোলোজি কিংবা ট্রিটিং স্ক্রিন অ্যান্ড ট্রিট তথা একই সময়ে শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে।
চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে।
(ক) প্রতিটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালে কলপোস্কপি ক্লিনিক তৈরি
(খ) বিভাগীয় ৮টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ক্যানসার সেন্টারে
চিকিৎসকদের কলপোস্কপি, ক্রিয়োথেরাপি, থার্মাল অ্যাবলেশন, লিপ প্রসিডিউর বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
(গ) ক্যানসারের সার্জারির জন্য আরও উচ্চতর প্রশিক্ষণদান।
(ঘ) এনজিও, সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজ তৈরি।
(ঙ) ক্যানসার রেজিস্ট্রি, মৃত্যুহার রেজিস্ট্রির মধ্যে সংযোগ স্থাপন।
(চ) রেডিও থেরাপি ও কেমোথেরাপির প্রসার।
(ছ) পেলিয়েটিভ সেবার প্রসার।
(জ) স্বাস্থ্যবিমার প্রবর্তন।
আসুন আমরা সবাই মিলে সচেতন হই ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে থেকে জরায়ুমুখ ক্যানসারমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে পৃথিবীর বুকে নতুন ইতিহাস রচনা করি।
লেখক: অধ্যাপক ও ইউনিট প্রধান, গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সদস্য সচিব, অনকোলজি কমিটি ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক সচিব, ওজিএসবি
- ট্যাগ:
- জরায়ুমুখ ক্যানসার

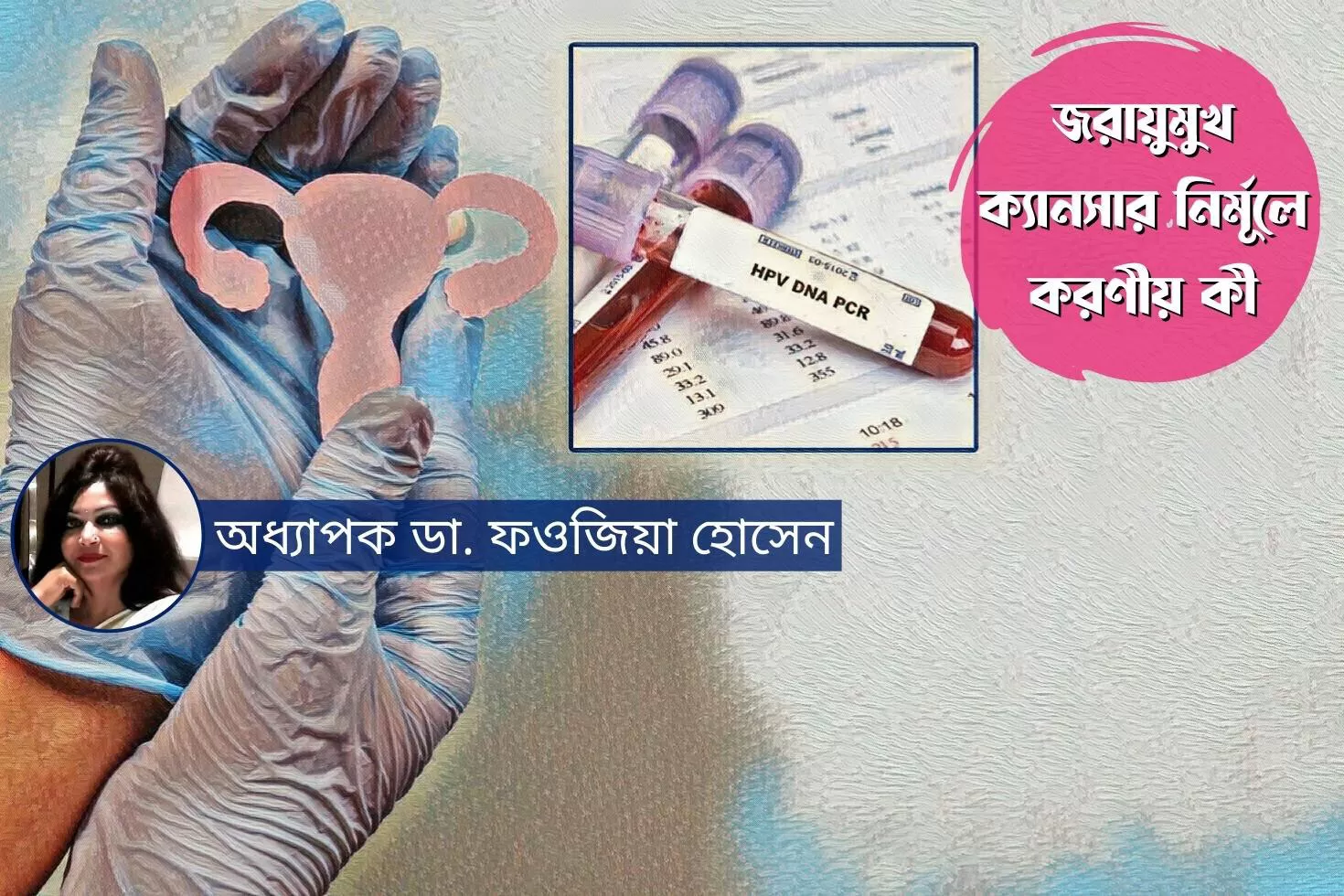



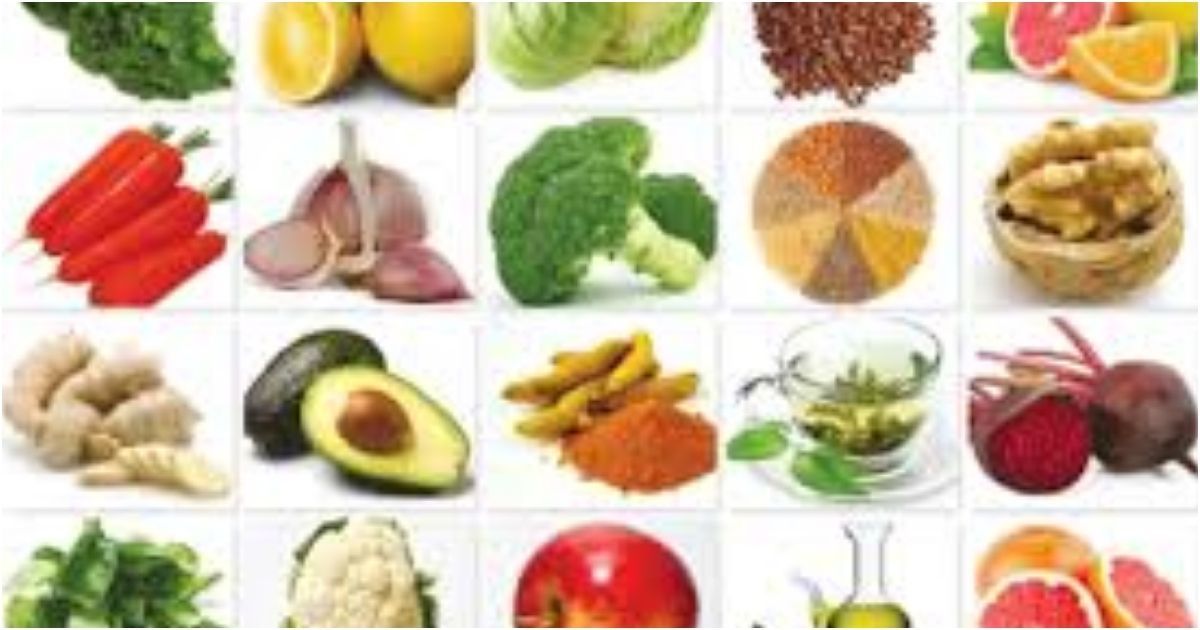

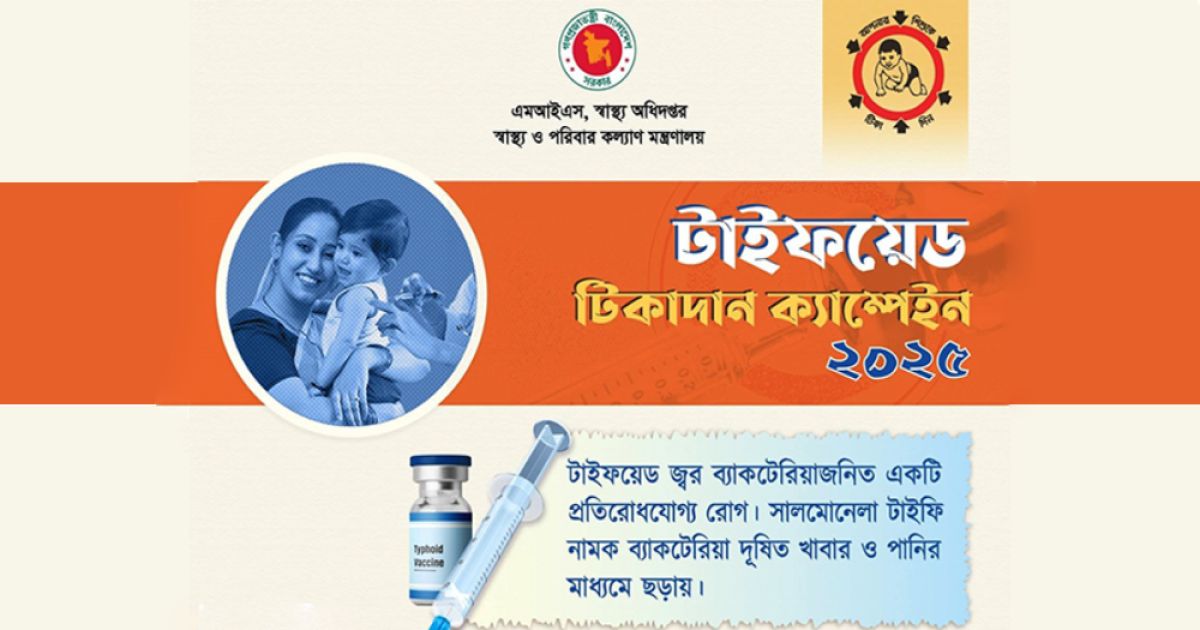











মন্তব্য