বাংলাদেশ তার উন্নয়ন অভিযাত্রার গৌরবময় অধ্যায় পার করছে। ‘সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রার বাংলাদেশ’ নির্বাচনি ইশতেহারটি যে এত স্বল্প সময়ে দেদীপ্যমান বাস্তবতা হয়ে ধরা দেবে তা কে-ইবা ভেবেছিল।
বাংলাদেশ তার ইতিহাসে একের পর এক উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে প্রতিনিয়ত গ্রহণ করছে নানামুখী উন্নয়ন কৌশল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধারাবাহিক নেতৃত্বে একদিকে অর্থনৈতিক ও শিল্প খাতে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে অবকাঠামো ও সামাজিক খাতে দ্রুত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
গত এক যুগে বাংলাদেশ একদিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, অন্যদিকে উন্নয়ন এজেন্ডায় জনগণের অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ‘উন্নয়ন বিস্ময়’ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শূন্য রিজার্ভ নিয়ে পথচলা শুরু করে ৭১৯ কোটি টাকার প্রথম বাজেট উপস্থাপন করেছেন। আর আজ তাঁর কন্যার হাত ধরে সে বাজেট এখন ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.১৫ শতাংশ, যা এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ। কোভিড-পূর্ব সময়কাল পর্যন্ত গত পাঁচ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ শতাংশের বেশি।
একদিকে সরকার অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যে গ্রহণ করছে নানামুখী উন্নয়ন প্রকল্প, অন্যদিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বৃহৎ উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপাশি একযোগে পরিচালিত হচ্ছে সমাজের পিছিয়ে পড়া দুস্থ, অসহায় এবং ছিন্নমূল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে নানামুখী কর্মসূচি।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন ভাবনার অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে আশ্রয়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহায়ণের সঙ্গে কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, শিক্ষা, পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম যুক্ত হয়েছে। একটি গৃহ কীভাবে সামগ্রিক পারিবারিক কল্যাণে এবং সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে তার অনন্য দৃষ্টান্ত ‘আশ্রয়ণ’ প্রকল্প।
যুগলবন্দি: বৃহত্তম জাতীয় প্রকল্প এবং গ্রামীণ উন্নয়ন
উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবকাঠামো খাতের ইতিবাচক ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে সরকার দেশের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে।
বর্তমানে ৪৭.৮৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ‘ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে’ এবং কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশের সব মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যার আওতায় ইতোমধ্যে ৪৫৩ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক চার লেনে উন্নীত হয়েছে।
একই সঙ্গে বাস্তবায়িত হচ্ছে ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতু প্রকল্প, ১ লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, রামপালে ১৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট, মাতারবাড়িতে ২×৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট, ১৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প এবং ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প। এ ছাড়াও ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এলএনজি টার্মিনাল ও গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম চলমান।
দ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে ৪০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প ও ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দোহাজারী-রামু হয়ে কক্সবাজার ও রামু-মিয়ানমারের কাছে ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প। এ ছাড়া সমগ্র দেশে একযোগে নির্মাণ করা হচ্ছে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের একটি অনন্য সাধারণ কর্মসূচি। বর্তমান সরকারের বিগত ১০ বৎসরে (২০০৯-১০ হতে ২০২০-২১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ছিল ১ লাখ ১৪ হাজার কোটি টাকার বেশি। এই একই সময়ে সেতু বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪ লাখ কোটি টাকার বেশি। বিগত ১০ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বরাদ্দ ছিল ২ লাখ কোটি টাকার বেশি।
বর্তমান সরকার বিগত ১২ বছরে (২০০৯-২০২১) দেশে মোট ৬৩,৭৪৭ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ সময়ে ৩,২১,৩২২ মিটার নতুন ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির সঞ্চালন, দ্রুত বিকাশ, ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪১ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
অন্যদিকে সরকার দরিদ্র, অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ রেখেছে ১ লাখ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা (২০২১-২২), যা বাজেটের ১৭.৮৩ শতাংশ এবং ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ৮ গুণ বেশি। জাতির পিতার দেখানো পথ ধরেই ১৯৯৭-৯৮ সালে দেশে প্রথমবারের মতো বয়স্ক ভাতা এবং ১৯৯৮ সালে বিধবা ভাতা, স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের জন্য ভাতাসহ নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করা হয়।
২০১০-১১ অর্থবছরে ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি এবং ২০১৩-২০১৪ সাল থেকে সব বীর মুক্তিযোদ্ধাকে প্রদান করা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা যা ১২ হাজার থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ২০ হাজার টাকা। সবশেষ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুসারে, দেশের ৫ কোটির বেশি মানুষ কোনো না কোনো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় চলে এসেছে। আমাদের দেশে ৪৪ লাখ ব্যক্তি বয়স্ক ভাতার আওতাধীন, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, দুস্থ মহিলা ভাতার আওতায় ১৭ লাখ এবং অসচ্ছল, প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন ১৫ লাখ ৪৫ হাজার জন। প্রতিবছর ১ লাখ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হয়। এ ছাড়া হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জন্য রয়েছে ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ ভাতা।
এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অনগ্রসর উপকারভোগীর সংখ্যা ৭১,৩২০ জন। শুধু এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট দেয়া হয় ৯৭,০৮৩ জনকে (২০২০-এর হিসাব)। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলাকালীন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫) দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশ ও চরম দারিদ্র্যের হার ৭.৪ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
২০০৫-০৬ অর্থবছরে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ৪০ ও ২৫.১ শতাংশ, কিন্তু বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের ফলে এ হার বর্তমানে ২০.৫ ও ১০.৫। বর্তমান কোভিডকালে দুই কিস্তিতে ৭০ লাখ দরিদ্র পরিবারকে (২৫০০ টাকা হারে) মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে নগদ অর্থসহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
কেউ পিছিয়ে থাকবে না
বাংলাদেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষের আবাসন নিশ্চিতকল্পে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার অন্যতম উদ্ভাবন হচ্ছে ‘আশ্রয়ণ প্রকল্প’। একটি ঘর একটি ছিন্নমূল পরিবারের দারিদ্র্য হ্রাসসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এটি এখন প্রমাণিত। প্রতিটি নিরাপদ গৃহ পরিবারের সবাইকে করে তোলে আস্থাবান, প্রত্যয়ী এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগী।
১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রথম ‘আশ্রয়ণ’ প্রকল্প চালু করে গৃহহীন, ছিন্নমূল এবং অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে তাদের জীবনমান উন্নয়নে ঋণদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ আয়বর্ধক কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ত করেন। তাঁর দেখানো পথেই ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে ৩৮৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,৯৮,২৪৯টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। কিন্তু মুজিববর্ষে এসে দ্রুততম সময়ে গৃহহীন ও ভূমিহীন মানুষকে গৃহ প্রদানের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত গৃহায়ণ কর্মসূচিকে তিনি নতুনরূপে উপস্থাপন করেন।
জাতির সামনে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পকে অধিকতর যুগোপযোগী ও টেকসই করার লক্ষ্যে তিনি নতুন ডিজাইনের গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্যারাক নির্মাণ কর্মসূচির পাশাপাশি প্রতিটি দুস্থ পরিবারের জন্য ২ শতক জমি প্রদানসহ দুই কক্ষবিশিষ্ট গৃহ, প্রশস্ত বারান্দা, রান্নাঘর ও টয়লেট নির্মাণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারি ২০২১ সালে তিনি প্রথম পর্যায়ে ৬৯ হাজার ৯০৪টি পরিবারের মালিকানা স্বত্বসহ গৃহ প্রদান করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ জুন, ২০২১ সালে ৫৩ হাজারের অধিক পরিবারকে অনুরূপভাবে গৃহ প্রদান করা হয়।
একই সঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক পরিবারকে গৃহ প্রদানের ঘটনা পৃথিবীতে আর কোনো দেশে সম্ভব হয়নি। সমগ্র বাংলাদেশের জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে এসব গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে তারা খাস জমি চিহ্নিতকরণ ও অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধার করে গৃহহীনদের আবাসনের ব্যবস্থা করছে। এ কাজে কখনওবা তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে জমি উদ্ধার করেছে।
প্রকল্পের বিশেষত্ব
১. ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির ও গৃহের মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। পুনর্বাসিত পরিবার যেন ভবিষ্যতে মালিকানাসংক্রান্ত বিরোধে জড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জমির মালিকানা স্বত্বের রেজিস্টার্ড দলিল/কবুলিয়ত, নামজারি সনদ ও দাখিলাসহ সরেজমিনে দখল হস্তান্তর করা হয়।
২. পুনর্বাসিত পরিবারকে ৩ মাস (মেয়াদ) ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়।
৩. সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী, সামাজিক সুবিধা কর্মসূচির আওতায় মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতাসহ অন্যান্য কর্মসূচির সুবিধাপ্রাপ্তির বিষয়টি অগ্রাধিকারসহ বিবেচনা করা হয়।
৪. পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য ব্যবহারিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৫. সরকারি বিভিন্ন সংস্থা (যেমন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায়, মহিলা ও শিশু অধিদপ্তর, সমাজসেবা বিভাগ) থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া অন্যান্য সামাজিক সংস্থা ও এনজিওকেও এসব কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়।
৬. পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয় এবং প্রকল্প স্থানে নিরাপদ পানির জন্য টিউবওয়েলের সংস্থান করা হচ্ছে।
৭. পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য কমিউনিটি সেন্টার, প্রার্থনাঘর ও কবরস্থানসহ পুকুর খনন ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য রাস্তা নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে।
৮. প্রকল্প এলাকায় ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করা হচ্ছে এবং কৃষি কাজে গৃহহীনদের উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।
জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য আশ্রয়স্থল
বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করেন। তার দেখানো পথেই বঙ্গবন্ধুকন্যা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্দশা দেখে তাদের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। আওয়ামী লীগ নেতার দান করা জমিতেই শুরু হয় পুনর্বাসন কার্যক্রম। আর ১৯৯৭ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র দেশে শুরু করেন আশ্রয়ণ প্রকল্প।
সবশেষ অগ্রগতিসহ ব্যারাক ও একক গৃহে এ পর্যন্ত ৪,৪২,৬০৮টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীভুক্ত ৪,৮৩২টি পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। পাহাড়ে বসবাসরত ৮,১০৬টি পরিবারকেও গৃহ প্রদান করা হয়েছে। তাদের পেশা উপযোগী প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
পুনর্বাসনের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সহায়তায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে প্রকল্প স্থান বাছাইসহ ভূমি উন্নয়ন ও উন্মুক্ত পদ্ধতিতে স্থানীয় জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে উপকারভোগী নির্বাচন এ কার্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কক্সবাজারের খুরুশকুলে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য ২০টি ভবনে ৬৪০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এখানে আরও ৩,৭৬৯টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ১১৯টি ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান। এটিই জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য পৃথিবীর বৃহত্তম আবাসন।
এসডিজি (টেকসই অভীষ্ট) অর্জনে গৃহ নির্মাণের ভূমিকা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জাতিসংঘের Sustainable Goals এর লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে গৃহায়ন কার্যক্রমের বিশেষ সংযোগ রয়েছে। শুধু গৃহ নির্মাণের ফলে মানুষের জীবনের টেকসই উন্নয়নের নানামুখী লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। গৃহায়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার প্রাপ্তি যেমন সম্পৃক্ত, তেমনি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহেও ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.৪
২০৩০ সালের মধ্যে সব নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত (সংস্থাপন) জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা-সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ক্ষুদ্রঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে।
মন্তব্য: আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা রেজিস্ট্রি দানপত্রমূলে সরকার কর্তৃক প্রদান করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রতিবন্ধী, দুস্থ, বিধবা, স্বামী নির্যাতিতা, বয়স্ক নারী-পুরুষ ও তাদের পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.৫
দারিদ্র্য ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাতসহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ঝুঁকি কমিয়ে আনা।
মন্তব্য: চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবজনিত কারণে গৃহহারা ৪,৪০৯টি দরিদ্র পরিবারের জন্য কক্সবাজারে খুরুশকুলে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। এখানে তাদের পুনর্বাসনের জন্য ১৩৯টি পাঁচতলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান। এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প। ইতোপূর্বে ২০টি ভবনের কাজ সম্পন্নপূর্বক ৬৪০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এ ছাড়া চাহিদা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন জেলায় আরও ৫০টি বহুতল ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন।
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২.৩
ভূমি এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণে নিরাপদ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপালনকারী ও অন্যান্যের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা। এটি অর্জনের জন্য সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।
মন্তব্য: যেসব উপাদান দারিদ্র্য জিইয়ে রাখে, পুষ্টিহীনতা তার মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের পুষ্টিমান অনেকটাই নির্ভর করে পানি, পয়োনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতার গুণগত মানের ওপর। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহ নতুন ঘরে যেমনি পানি, পয়োনিষ্কাশন সুবিধা পাচ্ছে, তেমনি গৃহ আঙিনায় কৃষিজ উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত রয়েছে। এ ছাড়া হাঁস-মুরগি চাষ ও পশুপালন কর্মেও তারা যুক্ত আছে। এ জন্য সরকারি সংস্থার মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ ও ঋণসহায়তা দেয়া হচ্ছে। সমবায় ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকার পুকুরে মাছ চাষ করা হচ্ছে। পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণের জন্যও প্রশিক্ষণ ও ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৩
সব বয়সী সব মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।
মন্তব্য: পুনর্বাসিত পরিবারসমূহ ইতোপূর্বে যারা ভাসমান জীবনযাপন করতেন, তারা নানা রকম সংক্রামক ব্যাধি যেমন- ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা ও পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতেন। এ ছাড়া সুবিধাবঞ্চিত ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রজননসংক্রান্ত, মাতৃত্বজনিত, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্যবিষয়ক অসুস্থতার কারণে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতেন।
গৃহায়ণের ফলে তারা বিরূপ এবং প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছেন। একইভাবে তারা গুরুত্ব না দেয়া কিছু উষ্ণমণ্ডলীয় রোগ বা neglected tropical diseases (NTD) থেকে তারা মুক্তি পাচ্ছেন সুপেয় পানি, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত হওয়ার কারণে। ঘরে অবস্থানের কারণে শিশুদের টিকা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া প্রজনন ও মাতৃস্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন সেবা প্রদান সহজলভ্য হয়েছে।
নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক গৃহ ভিজিট করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীসহ অন্যান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন।
একই সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে নারী ও শিশুরা নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানোর ক্ষেত্রে প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আশ্রয়ণ এলাকাগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় সময়মতো স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিত করাও অনেক সহজ হবে। আশা করা যায় যে, এর ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুও হ্রাস পাবে।
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৫.ক
অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সব ধরনের সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন।
মন্তব্য: এ প্রকল্পে উপকারভোগী প্রতিটি ভূমিহীন পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে জমির মালিকানা রেজিস্ট্রি দলিলমূলে প্রদান করা হয়ে থাকে। একই সঙ্গে যৌথ নামে নামপত্তন, খতিয়ান ও দাখিলা প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে প্রথাসিদ্ধ আইনি কাঠামোর বাইরে উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের সন্তানদেরও সমান অধিকার নিশ্চিত হবে।
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.২
পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতির অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং নারী ও বালিকাসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো।
মন্তব্য: দিনমজুর, ভবঘুরে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পূর্বে মলত্যাগের কোনো সুনির্দিষ্ট স্থান ছিল না। প্রান্তিক পর্যায়ে অনেকে খোলা স্থানেও মলত্যাগ করত। বর্তমান প্রকল্পে প্রতিটি গৃহের সংলগ্ন ৪ ফুট দৈর্ঘ্য × ৪ ফুট প্রস্থ টয়লেট আছে এবং গৃহসংলগ্ন টিউবওয়েল থেকে প্রাপ্ত পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ফলে আশ্রয়ণের সুবিধাভোগীরা নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় স্যানটিশেন সেবা পাবে। সরকারি সংস্থা ও এনজিওর মাধ্যমে গৃহীদের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণও দেয়া হচ্ছে।
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১০.২
বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান) ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে সবার ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্তন।
মন্তব্য: ভূমিহীন এবং গৃহহীন যেকোনো বয়সের মানুষই এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। তবে প্রবীণ, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও স্বামী পরিত্যক্তাদের অসহায়ত্বের বিষয়টি বিবেচনায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সমতল ছাড়াও পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগণকেও এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে।
এ পর্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় এথনিকদের জন্য ৮১০৬টি গৃহ ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ৪৮৩২টি গৃহ বিতরণ করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন এলাকায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া পুকুর খননকৃত এলাকায় সমবায় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হচ্ছে। সরকারি সহায়তায় বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ ব্যবসা বা কৃষি কাজের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়াও কুষ্ঠ রোগীদের জন্য বান্দাবাড়ি আশ্রয়ণ প্রকল্প, হিজড়া সম্প্রদায়ের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলায় উল্লাপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প, দিনাজপুরের পার্বতীপুর এলাকায় কয়লাখনি শ্রমিক, বরগুনা তালতলি এলাকায় রাখাইন পরিবারের জন্য বিশেষ টংঘর ও নীলফামারীর সদর উপজেলায় হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫
দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে পানি সম্পৃক্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা।
মন্তব্য: বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে দৃশ্যমান সম্পদ যেমন- ঘরবাড়ি, ক্ষেতের ফসল, গবাদিপশুসহ অন্যান্য অবকাঠামো। সেটা বিবেচনা করে প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রতিটি গৃহ তুলনামূলক উঁচু স্থানে নির্মিত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাঙন বা অতিবৃষ্টির কারণে যাতে গৃহের ক্ষতি না হয় বা জনগণের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। এমনকি প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাটের জন্যও বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে যাতে আবাসস্থলসমূহ দুর্যোগ সহনীয় হয়ে ওঠে।
অস্পৃশ্যতার দেয়াল ভেঙে
কুষ্ঠ রোগীদের জন্য বান্দাবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্প: বাংলাদেশের বৃহত্তর রংপুর এলাকায় কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক। পরিবার পরিত্যক্ত এসব কুষ্ঠ রোগীর বাঁচার একমাত্র অবলম্বন ছিল ভিক্ষাবৃত্তি। নিজ এলাকায় মানুষ কাছে আসতে চাইত না বলে ঠিকমতো ভিক্ষাও পেত না কুষ্ঠ প্রতিবন্ধীরা, ফলে তারা পাড়ি জমায় ঢাকা শহরে।
মৌলিক অধিকার বঞ্চিত কুষ্ঠ রোগীরা ঢাকা এসে কমলাপুর রেলস্টেশন, আগারগাঁও এলাকার পঙ্গু হাসপাতালসংলগ্ন বস্তি এলাকায় শরীরের খসে পড়া অংশ দেখিয়ে ভিক্ষা করত। ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কুষ্ঠ রোগ নির্মূলে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২০০০ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকা থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে ভাওয়ালের গজারি বনে ঘেরা কালিয়াকৈর উপজেলার বোয়ালী ইউনিয়নের বান্দাবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্পে মাথা গোঁজার ঠাঁই পায় কুষ্ঠ প্রতিবন্ধী পরিবারসমূহ। আশ্রয়ণ প্রকল্পটি হয়ে ওঠে তাদের বেঁচে থাকার নতুন আশ্রয়।
প্রকল্পটিতে ৭টি ব্যারাকে ৭০টি গৃহহীন কুষ্ঠ রোগী পরিবারকে পুর্নবাসন করা হয়। পুর্নবাসনের পর তাদের কর্মসংস্থানের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর একদিকে যেমন তাদের কুষ্ঠ রোগ ভালো হয়েছে, অন্যদিকে তারা অসম্মানজনক ভিক্ষাবৃত্তি থেকে সরে এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়েছে। অনেকেই সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন।
হিজড়া সম্প্রদায় পুর্নবাসন: সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলায় বাস্তবায়িত হাটিকুমরুল আশ্রয়ণ প্রকল্পটি অন্যান্য প্রকল্প হতে একটু ভিন্ন। হাটিকুমরুল আশ্রয়ণ প্রকল্পটিতে পুনর্বাসন করা হয়েছে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর হিজড়া জনগোষ্ঠীকে। প্রকল্পটিতে ৪টি সেমিপাকা ব্যারাকে ২০টি তৃতীয় লিঙ্গের পরিবারকে পুর্নবাসন করা হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করেছেন। তাদের জীবনমান উন্নয়নে দেয়া হয়েছে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ এবং সেলাই মেশিন। গড়ে তোলা হয়েছে গরুর খামার। তাছাড়া হাঁস-মুরগি, কবুতর পালন ও শাকসবজি উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণ: আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৮টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবার এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার ১৭৬টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারকে বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় ৩৬৬টি বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তিন পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জন্য সর্বমোট ৫৮০টি বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।
এ ছাড়া মুজিববর্ষে রাঙ্গামাটি জেলায় ৭৩৬টি, বান্দরবান জেলায় ২,১৩৪টি এবং খাগড়াছড়ি জেলায় ৯৬৮টি গৃহহীন পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে।
দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কয়লাখনির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পুনর্বাসন: দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ৩১৮টি পরিবারের পুনর্বাসনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাক্রমে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দক্ষিণ পলাশবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্পে ৬৪টি পাকা ব্যারাক নির্মাণ করে ৩১৮টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী (রাখাইন) পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের টং ঘর নির্মাণ: বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় অসহায় রাখাইন সম্প্রদায়ের পরিবারের জন্য এ পর্যন্ত ২০টি টং ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছে।
ভিক্ষুক পুনর্বাসন: ভিক্ষুক পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার ভিক্ষুকদের জন্য ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৬৯১টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।
তাছাড়া নড়াইল জেলাকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণার অংশ হিসেবে নড়াইল জেলার তিন উপজেলায় ইতোপূর্বে (২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছর) ৩১১টি ভিক্ষুক পরিবারকে এবং মুজিববর্ষে আরও ২২টি ভিক্ষুক পরিবারকে অর্থাৎ মোট ৩৩৩টি ভিক্ষুক পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
হরিজন সম্প্রদায় পুনর্বাসন: নীলফামারী জেলার সদর উপজেলায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ১২টি ৫ ইউনিটবিশিষ্ট সিআই সিট ব্যারাক নির্মাণ করে ৬০টি হরিজন সম্প্রদায়ের পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প: মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত ৫তলা বিশিষ্ট ২০টি বহুতল ভবনে প্রথম পর্যায়ে ৬০০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে ৪০৬.০৭ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি করে ফ্ল্যাট উপহার দেয়া হয়েছে।
এ প্রকল্পের আওতায় ৫ তলাবিশিষ্ট ১৩৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করে ৪৪০৯টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন করা হবে। খুরুশকুল প্রকল্পটি বিশ্বের একক বৃহত্তম জলবায়ু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৩ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখে উদ্বোধন করেন। অবশিষ্ট ১১৯টি বহুতল ভবন ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ কর্তৃক পৃথক ডিপিপির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ‘বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা অর্জনে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
উপসংহার
এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সমন্বিত নীতিকাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রধান কারণ হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। একই সঙ্গে এসডিজিকে সমন্বিত করা হয়েছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০২১-২০২৫) সঙ্গে যা উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে বৃহৎ অবকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে একীভূত করেছে।
মুজিববর্ষে বিশেষ উদ্যোগে সমাজের ছিন্নমূল মানুষকে জমি ও গৃহ প্রদানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ‘যে আছে সবার পিছনে, পৌঁছাতে হবে তার কাছে আগে’- অগ্রাধিকার নীতি হিসেবে এটি গ্রহণের ফলে সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে।
বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্যের (শতকরা ১০. ৫ ভাগ) আওতাভুক্ত জনগণই গৃহায়ণ কর্মসূচির প্রধান উপকারভোগী। ফলে, স্বভাবতই দারিদ্র্য বিমোচনে এ প্রকল্প অনন্য সাধারণ। দেশের পিছিয়ে পড়া এলাকা এ কার্যক্রমের সুবিধা পাচ্ছে। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, চা শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, পরিবেশগত শরণার্থী, প্রতিবন্ধী, খনি শ্রমিক, কুষ্ঠ রোগী এবং অতি দরিদ্র নারীরা এ কর্মসূচির প্রধান উপকারভোগী।
এসব পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য উপার্জন ও উৎপাদনশীল সম্পদে তাদের প্রাপ্যতা বাড়াতে এবং ন্যূনতম শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির সংস্থান এ কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জিত হওয়া সম্ভব। এসডিজি ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নের ফলে অসমতা কমানো, বিভিন্ন সেবায় প্রবেশগম্যতা, বিদ্যুৎ ও নিরাপদ পানি প্রাপ্তি এবং নাগরিক মর্যাদাকেন্দ্রিক বাধা-বিপত্তির অবসান হবে। একই সঙ্গে জেন্ডার ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকেন্দ্রিক অসমতাগুলো দূরীভূত হবে। শুধু গৃহায়ণের ফলেই কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। গুচ্ছভিত্তিক আবাসনের ফলে সর্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা একই স্থান থেকে দেয়া হবে। ফলে, পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা সহকারীরা গ্রামীণ এলাকায় নিয়মিত উপকারভোগীদের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে সেবা দিতে পারবেন।
স্থানীয় পর্যায়ে নির্মাণসামগ্রী সরাসরি গ্রামীণ বাজার থেকে সংগ্রহের ফলে নির্মাণ ব্যয় তুলনামূলক কম হচ্ছে এবং একই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতিও চাঙা হচ্ছে। এই একটি প্রকল্পের মাধমেই পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের নব দিগন্ত সূচনা হয়েছে বাংলাদেশের আকাশে।
মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

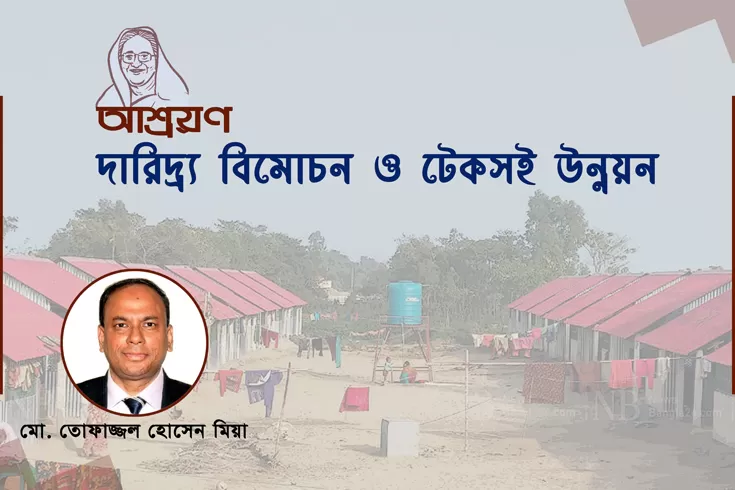


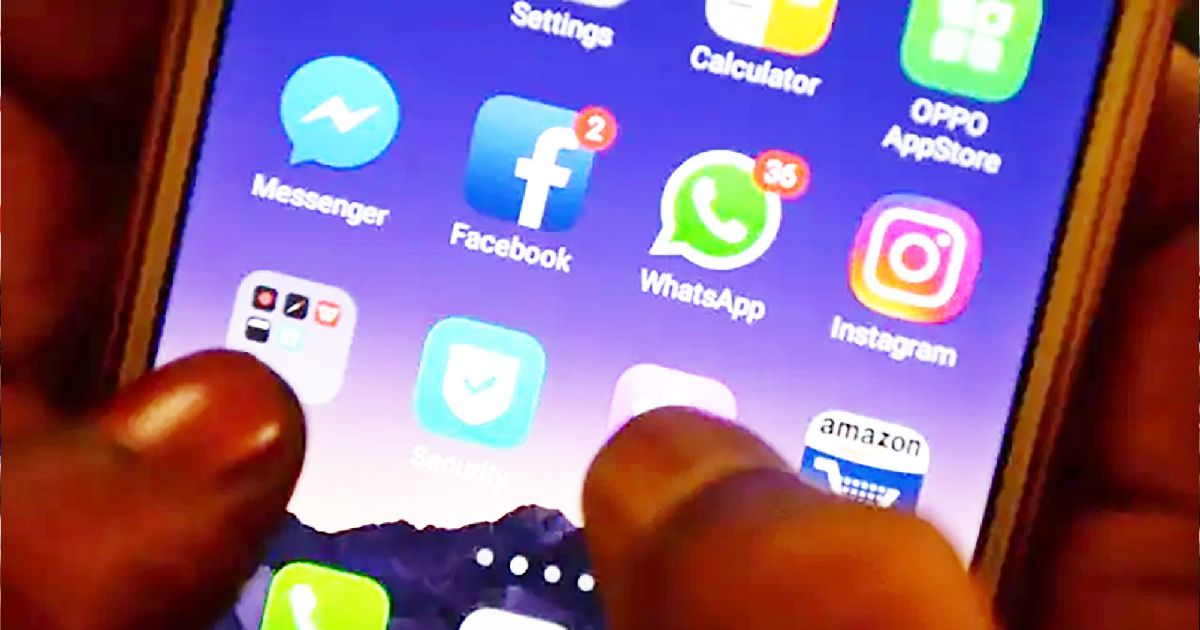







মন্তব্য