ষাটের দশক। কঠিন সামরিক শাসনের জাঁতাকলে পূর্ববাংলা নিষ্পিষ্ট। স্বৈরাচারী সামরিক শাসক, সেসময়ে ‘লৌহমানব’ বলে পরিচিত পাকিস্তানি জেনারেল ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের অত্যাচারে জর্জরিত সমগ্র পাকিস্তান, বিশেষ করে পূর্ব বাংলা। আর এর প্রতিবাদে, সামরিক শাসনের আশু অবসানের দাবিতে ছাত্র-যুবসমাজ, গণতন্ত্রকামী সব রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা দেশের রাজপথগুলোকে দৃপ্ত পদভারে প্রকম্পিত করে চলেছেন। সামরিকশাসনের কঠোরতা থোড়াইকেয়ার করে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে তুলছেন। সরকার প্রতিশোধ নিচ্ছে হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে বিনাবিচারে আটক করে কারারুদ্ধ করার মাধ্যমে। ওই কর্মসূচি যেমন পাকিস্তান সরকার, তেমনই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী গ্রুপ) ব্যতীত অপর সব দলকেও আতঙ্কিত করে তোলে। তারা সরাসরি শেখ মুজিবকে পুনর্বার পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমন আখ্যায়িত করে। শেখ মুজিব চলে আসেন পূর্ব বাংলায়, ঢাকা নগরীতে।
দিন কয়েকের মধ্যে তিনি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদসহ প্রথম সারির কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতাসহ গ্রেপ্তার হলেন। শেখ মুজিব (তখনো তিনি ‘বঙ্গবন্ধু’ খেতাবে ভূষিত হননি) ব্যতীত অপর নেতৃবৃন্দকে প্রদেশের অপরাপর কেন্দ্রীয় কারাগারে বদলি করে দেয়া হয়।
মুজিব ভাই থেকে যান একা এক বিশাল ওয়ার্ডে। আমি ওই দফায় গ্রেপ্তার হই, ঠিক যেদিন পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয় তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, দুপুরবেলায়। খেতে বসেছিলাম দেড় বছর কারারুদ্ধ থাকার পর। আগের দিন মুক্তি পেয়ে বাসায় আসি। পরদিনই আবার সরকারি আতিথ্য নিতে হলো, স্ত্রী-সন্তানদের রেখে।
এবার গ্রেপ্তার জন্মদোষে। অর্থাৎ হিন্দুঘরে জন্ম নিয়েছিলাম তাই। পাকিস্তান সরকার যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে জরুরি অবস্থা দিয়ে ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’ জারি করে। পাশাপাশি নেতৃস্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের গ্রেপ্তার শুরু করে। অবশ্য ৮-৯ মাস পর অপর হিন্দুনেতাদের মুক্তি দেয়া হয়। আর আমরা যারা ন্যাপ-সিপিবি করতাম তাদের রেখে দেয়া হলো। খুশি হয়েছিলাম, বাঁচা গেল, কারণ রাজনৈতিক পরিচয়টা পুনরুদ্ধার হলো। কিন্তু মুক্তি কবে পাওয়া যাবে তা অনুমান করা যাচ্ছিল না। এমন সময় আমার স্ত্রী পূরবী মৈত্র এলেন আমাদের ইন্টারভিউ নিতে। উৎসাহিত করলেন আমাকে ল পরীক্ষা দিতে। রাজি হলাম, বললাম নতুন পাস করা আইনজীবীদের কাছ থেকে সিলেবাস জেনে নিয়ে কিছু বইপত্র পাঠাতে। তিনি পাবনায় ফিরে সাধ্যমতো বই সংগ্রহ করে পাঠালেন। আমাকে অনেক আগেই আরও কয়েকজন বন্দিসহ পাবনা জেলা করাগার থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বদলি করে দেয়া হয়েছিল। সেখানে গিয়েই পূরবী ইন্টারভিউ নেন।
যা হোক, পরীক্ষা দিতে হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে, তিনি নিয়মিত কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তা জানিয়ে ওই মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত করতে হয়। ওই অনুমতি পাওয়ার পর উচ্চতম কারা কর্তৃপক্ষের (ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস) কাছে দরখাস্ত করে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে আবেদন জানাতে হয়। এসব ফর্মালিটি শেষ হতে হতে কয়েক মাস লেগে গেল। সেই ফাঁকে পড়াশোনাও চলল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা জানানো হলো কর্তৃপক্ষকে। পরে আমাকে জানানো হলো, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের কারাগারগুলোর মধ্যে কেবল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং সেখানে আমাকে বদলি করা হলো। তখন তো যমুনা সেতু নির্মিত হয়নি। তাই ট্রেনে সিরাজগঞ্জ-জগন্নাথগঞ্জ ফেরিতে যমুনা পার হতে হতো। সরাসরি ট্রেনে রাজশাহী থেকে ঢাকার ইন্টার-ক্লাস টিকিটের যাত্রী। সাথি তিন বন্দুকধারী পুলিশ, যার মধ্যে একজন সম্ভবত জমাদার-জাতীয় ছিলেন। পুলিশ দেখে ট্রেনের যাত্রীরা কেউ ভাবত চোর-ডাকাত, কেউবা চোরাকারবারি প্রভৃতি। পরে কম্পার্টমেন্টের সবার ভুল ভাঙল যখন আমি একগাদা সংবাদপত্র কিনলাম এবং তাদের দু-একজনের সঙ্গে কথা বললাম। রাজবন্দি জানার পর কী যে সম্মান যাত্রীরা দিলেন তা স্মরণীয়। তবে সেই আমলের মতো রাজবন্দিদের সম্মান আজ নাকি বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। কারণ, সন্ত্রাসনির্ভর ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছে আমাদের রাজনীতি। এখান থেকে যখন নীতি-আদর্শ তিরোহিত হতে থাকে, তখন থেকে রাজবন্দিদের সম্মান-মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়।
যা হোক, আমার সঙ্গে সঙ্গে এসকর্ট করা পুলিশরা পর্যন্ত চা-নাশতা-মিষ্টি পেয়ে গেলেন যাত্রীদের কাছ থেকে। আরও পেলাম দামি সিগারেটের কার্টন (তখন ধূমপানের অভ্যাস ছিল রীতিমতো)। ঢাকা পৌঁছালাম পরদিন সকাল ৮টার দিকে। জেলখানায় যেতে আরও ঘণ্টা খানেক। তখন ফুলবাড়ী ছিল ঢাকার রেলস্টেশন। জেলখানায় গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই ডেপুটি জেলার, যিনি রাজবন্দিদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, এলেন। দেখি তিনি পূর্বপরিচিত। চমৎকার ব্যবহার। কাগজপত্র সব জমা নিয়ে এসকর্ট পার্টিকে বিদায় দিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে আমি কোন ওয়ার্ডে থাকতে চাই, তা জানতে চাইলেন। জানালাম, এবার পরীক্ষা দিতে এসেছি। তাই পরীক্ষা পর্যন্ত জেনারেল ওয়ার্ডে যাব না। আমাকে নিরিবিলি পড়াশোনা করতে হবে, তাই যেকোনো সিটে দিলে ভালো হয়।
অতঃপর আরও ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করার পর ডেপুটি জেলার নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সম্ভবত পুরোনো ২০ সেলে; সেখানে ঢোকার গেটমুখী একটি সেল আমার জন্য বরাদ্দ। ইতোমধ্যেই তা ধুয়েমুছে একটি লোহার খাট, চেয়ার-টেবিল, খাবার জল, গ্লাস দেয়া হয়েছে। বেলা অনুমান সাড়ে এগারোটা। কিছু কথাবার্তা বলে যাওয়ার সময় ডেপুটি জেলার বললেন, আপনার এ সেলগুলোতে প্রবেশের প্রধান দরজা সর্বদা বন্ধ থাকবে। ভেতরে হাঁটাচলা করবেন। বললাম, এটা তো শাস্তি। হেসে ডেপুটি জেলার উপায় নেই, বলেই চলে গেলেন। ওই দরজাটাও তালাবদ্ধ হয়ে গেল। স্নান সেরে বিছানা পেতে শুয়ে বিশ্রাম নিলাম। বেলা একটার দিকে দুপুরের খাবার এলো। খেয়ে লম্বা ঘুম। রাতে ট্রেন-স্টিমারে তো ঘুমাতে পারিনি তেমন একটা। বিকেল পাঁচটার দিকে এক সিপাই এসে ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে বলল, বাইরে এসে দেখুন আপনার জন্য একজন অপেক্ষা করছেন। তাড়াতাড়ি উঠে হাত-মুখ ধুয়ে মেইন দরজা খোলা পেয়ে বাইরে দেখি মুজিব ভাই দাঁড়িয়ে তার বিশাল বপু নিয়ে। হাতে সেই চিরচেনা পাইপ। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ন্যাপ নেতাকেও গ্রেপ্তার করল? ন্যাপ তো আইয়ুবের পক্ষে। আমিও হেসে বললাম, সে জন্যই তো আপনারও এক বছর আগে আমাকে ধরে এনেছে। মুজিব ভাই বললেন, আরও কাউকে ধরেছে নাকি? বললাম অনেককে। সংখ্যায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীর তিন গুণ হবে। খোঁজ নিয়ে দেখুন। উনি বললেন, বেশ চলুন এখন হাঁটা যাক।
মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ১৯৫৩ সালে, পাবনায় আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়াত বগা ভাইয়ের বাড়িতে। আমি তখন ছাত্র ইউনিয়ন করি। ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল নিয়ে গিয়েছিলাম তার কাছে, ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য সকল দলের (কমিউনিস্ট পার্টিসহ) একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি ও মওলানা ভাসানী উদ্যোগী ভূমিকা নেন। তিনি বলেছিলেন, মওলানা সাহেব ও তিনি এ ব্যাপারে একমত। তবে শহীদ সাহেব (হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী) ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে রাজি করানোর চেষ্টা চলছে। সেটা সফল হলে যুক্তফ্রন্ট হয়ে যাবে। আমরা বলেছিলাম, সফল তো হতেই হবে, নইলে আমরা ছাত্রসমাজ ছাড়ব না। এভাবে এরপর যতবারই তিনি পাবনা এসেছেন ততবারই সাক্ষাৎ হয়েছে, অন্তরঙ্গভাবে আলাপ-আলোচনাও হয়েছে। পাবনায় তখন ছাত্র ইউনিয়ন ছিল প্রধান ছাত্র সংগঠন, ছাত্রলীগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। ফলে তা বুঝতে পেরে সেভাবে তিনি গুরুত্ব দিতেন। মওলানা ভাসানীর তো কথাই নেই। তিনি তো ছাত্রলীগের চেয়ে ছাত্র ইউনিয়নকেই তার আপন বলে মনে করতেন, মূলত ছাত্র ইউনিয়নের অসাম্প্রদায়িক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সমাজতন্ত্রকামী নীতির জন্য।
১৯৬২ সালে বা এর কিছু পরে যখন এনডিএফ গঠিত হয়, তখন মুজিব ভাই শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পাবনা আসেন জনসভা করতে। সেই জনসভার শুরুতে উপস্থিত বিশাল জনতাকে সামাল দিতে মাইক আমার হাতে দেয়া হয়। আমরা মুহুর্মুহু স্লোগান তুলি মওলানা ভাসানীর মুক্তি, এক ইউনিট, সিয়াটো-সিন্টে চুক্তি বাতিল প্রভৃতি দাবিতে। নেতৃবৃন্দ ছিলেন সার্কিট হাউসে, আর জনসভা ওই ভবনের সামনে পাবনা স্টেডিয়ামে। নেতারা মঞ্চে এলে তাদের স্বাগত জানাই; আমরা দিচ্ছি জিন্দাবাদ প্রভৃতি স্লোগান; কণ্ঠে আরও ছিল মওলানা ভাসানীর মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদ ও এক ইউনিট বিরোধিতা। স্লোগানগুলো শুনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মনে মনে ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন। সে ক্ষোভের প্রকাশ ঘটালেন সভা শেষ হলে সার্কিট হাউসে ফিরে গিয়ে। সেখানে তিনি মুজিব ভাইকে ডেকে বললেন, ওই স্লোগানগুলো কেন এত দেয়া হলো? মুজিব ভাই বাইরে এসে বারান্দায় আমার কাছে কৌশল করে বিষয়টি জানতে চাচ্ছিলেন। বললাম, স্লোগানগুলোর প্রতিটি পাবনা এনডিএফ কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত। আপনি প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন মনসুর সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি তাই করলেন। মনসুর সাহেব স্বীকার করলেন। তা শহীদ সাহেবকে জানালে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন,‘What is their members?’ আমি তখন ওনার রুমের কাছাকাছি। তাই নিজেই জবাব দিলাম, ‘not less than Awami Leage.’... তিনি এ জবাব শুনে ফুঁসতে থাকলেন।
যা হোক, অতঃপর পাবনা থেকে পরদিন তাদের সঙ্গেই আমি উত্তরবঙ্গ যাব সংবাদ-এর পক্ষ থেকে তাদের ট্যুর কভার করার জন্য। সারা পথ ট্রেনে। নানান জায়গায় এনডিএফ নেতৃবৃন্দের এ সফর উত্তরবঙ্গের মানুষ ও বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের মনে সামরিক শাসনবিরোধী জোয়ারের সঞ্চার করে। আর সংবাদে আমার রিপোর্টটি দেখে মুজিব ভাই তো বেজায় খুশি। তিনি যাত্রাপথে সাংবাদিকদের খোঁজখবর নিতে তাদের কামরায় ছুটে আসতেন, কোনো সমস্যা আছে কি না জানতে চাইতেন। হাতে করে আনতেন সংবাদ ও ইত্তেফাক। ইত্তেফাকের বিশেষ সংবাদদাতার সামনেই বলতেন, সংবাদের রিপোর্টটিই হচ্ছে বেস্ট।
যা হোক, এবার জেলখানার প্রসঙ্গে চলে আসি। প্রায় আধা ঘণ্টা হাঁটতে হাঁটতে শেষে আমার লক-আউটের সময় এসে যাওয়ায় দুজন মিলে হাঁটা বন্ধ করতে হলো। মুজিব ভাই চলে গেলেন তার দেওয়ানি ওয়ার্ডে (বলা হতো দেওয়ানি ফটক)। গিয়ে তিনি দুখানি খবরের কাগজ পাঠিয়ে দিলেন। ওই পড়তে পড়তে আহারাদি শেষ করে সেদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়ে এক পেয়ালা চা মুখে দিতেই দরজার ওপাশে মুজিব ভাই এসে হাজির। বেরিয়ে পড়লাম হাঁটতে। মুজিব ভাই দেশের কোনো খবর জানা আছে কি না, ঢাকায় আমার পক্ষে লোকজন কী বলল, জানতে চাইলেন। আমি জানালাম, ক্রমেই মানুষ আইয়ুব সরকারের বিরোধী হয়ে উঠছে এবং ছয় দফার সমর্থনে এসে শামিল হচ্ছে। শিগগিরই একটা বড় রকমের বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে বলে মনে হলো, যদি আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ যৌথভাবে আহ্বান জানায়। তিনি বললেন, যৌথভাবে আহ্বান করা সম্ভব হবে কি না জানি না, তবে আওয়ামী লীগ তাতে আহ্বান জানায় সে চিন্তায় আছি। যে ভয়ংকর অত্যাচারী শাসক সে, তাই সংগঠিত হতে সময় লাগতে পারে। তবে উভয়ের মধ্যে কথা থাকল দলীয় উৎস থেকে কোনো গোপন খবর এলে তা আমরা পরস্পর রক্ষা করব।
ন্যাপ তখনো অবিভক্ত, যদিও ভেতরে ভেতরে রুশ-চীন মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে ভাঙনের সুর বেজে চলছিল। বাংলাদেশে যারা চীনের মতাদর্শের সমর্থক ছিলেন, জাতীয় রাজনীতিতে তারা সামরিক শাসক আইয়ুবকে সমর্থন দিয়ে বসায় জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। অপরপক্ষে ন্যাপের বিশাল অংশ সমর্থন করত রুশ মতাদর্শ এবং জাতীয় রাজনীতিতে তারা সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরতন্ত্রবিরোধী, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী। তাই দেখা গেল চীনপন্থি নামে অভিহিতরা উগ্র আওয়ামী লীগবিরোধী; অপরপক্ষে রুশপন্থিরা আওয়ামী লীগের বহু দিকের বিরোধী হলেও গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠায় নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রত্যয়ী। ১৯৬৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাপ বিভক্ত হয়। চীনপন্থিরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এবং রুশপন্থিরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল ওয়ালী খানের নেতৃত্বে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হয়। স্বল্পকালের মধ্যেই এটি সমগ্র পাকিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তর রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।
বিরোধ দেখা দেয় মুজিব ভাইয়ের ছয় দফা কর্মসূচি প্রশ্নের। চীনপন্থিরা আইয়ুবের সুরে ওই কর্মসূচিকে মার্কিনি ষড়যন্ত্র এবং পাকিস্তানের সংহতিবিরোধী বলে প্রচার করে। আর রুশপন্থিরা একে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের অনুসারী বলে তার প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু ১৯৬৬ সালে আনুষ্ঠানিক বিভক্তি না হওয়ায় রুশপন্থি ন্যাপ নেতারা ব্যক্তিগতভাবে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে ছয় দফা কর্মসূচিতে সমর্থন জানান। এ কথা মুজিব ভাইকে খোলামেলা বলে আমি নিজেও সেই মতের অর্থাৎ রুশপন্থি মতবাদের অনুসারী বলে উল্লেখ করলে তিনি বিস্মিত ও আনন্দিত হন। যা হোক, এভাবে দিন চলতে থাকল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। ঘোষণা করা হলো ৭ জুন আওয়ামী লীগ বন্দিমুক্তি ও অপরাপর দাবিতে হরতাল আহ্বান করেছে। খবরটি সংবাদপত্র মারফত আমরা জানতে পেলাম। দিবসটি ছয় দফা দিবস হিসেবেও কোনো কোনো সংবাদপত্রে উল্লিখিত হয়।
ইতোমধ্যে মে মাস থেকেই আমার ল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ৭ জুন একটি পরীক্ষা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই জানিয়ে রেখেছে। দিনটি যতই নিকটে আসতে লাগল, আওয়ামী লীগের ওপর সরকারি নির্যাতন-নিপীড়নও বাড়তে থাকল। ওই দিন হরতাল, মিছিল ও জনসভার কর্মসূচি ছিল। সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই সন্ধ্যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়ালের বাইরে থেকে সহস্র কণ্ঠে যখন স্লোগান ধ্বনিত হতো জয় বাংলা, জাগো বাঙালি জাগো- কারাপ্রকোষ্ঠে লকআপে বসেও আমরা উজ্জীবিত হতাম। এভাবে ৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক বরাবর দরখাস্ত করলাম যেহেতু জনগণ ৭ জুন হরতাল বা কর্মবিরতি ডেকেছে, তাই তার সমর্থনে আমি ওইদিনকার পরীক্ষা দিতে বিরত থাকব। জমাদারের হাতে দরখাস্ত দিয়ে অফিসে পাঠালাম। কিন্তু জমাদার অফিসে যাওয়ার পথে মুজিব ভাইয়ের ওয়ার্ডে গিয়ে সালাম জানাতেই তিনি দরখাস্তটি পড়ে জমাদার সাহেবকে বলে পাঠালেন, আমি যেন দরখাস্তটি প্রত্যাহার করে নিই, কারণ পরীক্ষার সঙ্গে সারা জীবনের ক্যারিয়ারের প্রশ্ন জড়িত। আন্দোলনের জন্য তো সারাটি জীবনই রয়েছে। আমি বিনয়ের সঙ্গে তার কথা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললাম, জনগণ আন্দোলনে থাকবে আর আমি নিজের ক্যারিয়ারের জন্য আরামে বসে পরীক্ষা দেব তা হবে না। দরকার হলে পরের বছর পরীক্ষা দেব- এই বলে জমাদার সাহেবকে দ্রুত দরখাস্তটি অফিসে নিয়ে জমা দিতে বললাম। ছুটে এলেন ডেপুটি জেলর। তাদেরও একই অনুরোধ। আমি তা মানতে অপারগতা জানিয়ে দ্রুত দরখাস্তটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বললাম। তারা অফিসে ফেরত গিয়েই দরখাস্তটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছানোর জন্য পাঠিয়ে দিলেন।
বিকেলে হাঁটার সময় মুজিব ভাই প্রসঙ্গটি তুলে বললেন, কাজটি কিন্তু ভালো হলো না। আমার ভিন্নমত পুনরায় তাকে জানালাম। তিনি বললেন, ছাত্রলীগের কোনো নেতা তো পরীক্ষা দেয়া থেকে বিরত থাকবে না। সেখানে অন্তত নিজদলের অনুমতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। বললাম, তারাও তো সম্ভবত আপনার অনুরূপ পরামর্শই দিতেন। পরে বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘আসলে আমার তো ছয় দফা না, এক দফা। স্বাধীন বাংলা’। উত্তরে বললাম, পারবেন না। কারণ আপনারা কেবল তো আমেরিকামুখী। তারা কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কদাপি সমর্থন করেনি, করবেও না। হেসে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমেরিকাই বটে তবে ভায়া ইন্ডিয়া।’ বললাম, ইন্ডিয়ার কিছু লবি আছে, তাই তাদের মাধ্যমে রুশ শরণাপন্ন হোন।’ উত্তরে তিনি বললেন, দেখা যাক।’ অতঃপর ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ হলো। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগার থেকে তা প্রত্যক্ষ করলেন।
১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি বিজয়ীর বেশে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো এক দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি পাবনা সফরে এলেন। পাবনাবাসীর পক্ষ থেকে তাকে হেলিকপ্টার থেকে নামার পর প্রায় হাজার খানেক অভ্যর্থনাকারীর অন্যতম হিসেবে পাবনা স্টেডিয়ামে আমিও লাইনে দাঁড়িয়ে, তবে একটু পেছনের দিকে তৃতীয় সারিতে।
বঙ্গবন্ধু রুশপ্রদত্ত হেলিকপ্টার থেকে নেমে পুলিশের আনুষ্ঠানিকতা শেষে অভ্যর্থনাকারীদের প্রথম সারি থেকে করমর্দন করতে লাগলেন। হঠাৎ আমার ওপর চোখ পড়তেই লাইন ও কর্ডন ভেঙে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। দীর্ঘ আলিঙ্গন শেষে বললেন, কী, বলেছিলাম না দেশ স্বাধীন করে ছাড়ব? উত্তরে আমিও বললাম, আপনার মার্কিনি কেবলার সহযোগিতায় বিজয় অর্জিত হয়নি, হয়েছে আমার বলা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায়।’ হেসে বললেন, কথাটি পাঁচ বছর আগে ঢাকা জেলে হয়েছিল। আজও মনে আছে দেখছি।’ বললাম, ভুলেই গিয়েছিলাম, আপনিই এত দিন পরে তা মনে করিয়ে দিলেন।’
এবারে আবার ফিরে যাই সেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। একদিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। তবে দিন-তারিখ মনে নেই। বিকেল চারটার দিকে একটা স্লিপ হাতে হেড ওয়ার্ডার এলেন, আমার হাতে দিলেন দেয়ার জন্য । দেখি তাতে লেখা আছে- ফর ইন্টারভিউ মি. রণেশ মৈত্র, সিকিউরিটি প্রিজনার।’ জিজ্ঞেস করলাম, কার সঙ্গে ইন্টারভিউ? হেড ওয়ার্ডার বলেন তা কিছু বলেনি।’ কাপড়-চোপড় পরে ডিটেনশন অর্ডারটা হাতে নিয়ে চললাম রাজবন্দিদের ইন্টারভিউ রুমে। ঢুকতেই দেখি, মুজিব ভাই বসা। সামনে বসে আছেন এক মহিলা তার কিশোরী কন্যাকে নিয়ে। তবে দুজনের কাউকে চিনি না। আর এক কোনায় বসে আছেন আমার বাল্যবন্ধু ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম। তিনিই এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার দিকে পা বাড়াতেই মুজিব ভাই একটু দাঁড়াতে বলে ভাবির দিকে ইশারা করে বললেন- ‘আপনার ভাবি।’ আমি তাকে সশ্রদ্ধ সালাম জানালাম। আর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমাদের মেয়ে হাসিনা।’ বলেই মেয়েকে বললেন, ইনি তোমার চাচা, রণেশ মৈত্র। পাবনার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা। বয়সে জুনিয়র হলেও আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। সালাম করো।’ হাসিনা এগিয়ে আসতে নিলে বললাম, তুমি অনেক বড় নেতার মেয়ে, নিজেও ভাবিষ্যতে বড় হবে আশা করি। সেইভাবে নিজেকে গড়ে তোলো।’
অতঃপর ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি আমার আটকাদেশ বেআইনি দাবি করে হাইকোর্টে রিট করতে চান। সম্মতি চাইলে তা দিলাম। আটকাদেশটি প্রয়োজন বলায় পকেটে থাকা আটকাদেশও ডেপুটি জেলারের মাধ্যমে দিলাম। বাইরের কিছু খবরাখবর আসার ইঙ্গিতে শুনলাম। মুজিব ভাই আমীর-উল ইসলামকে বললেন, ‘শোনো আমীরুল, টাকা যা লাগে আমি দেব, তুমি রিটটা ভালো করে করবে। দরকার মনে করলে বড় কোনো সিনিয়র আইনজীবীকেও সঙ্গে নিও। ওনার দ্রুত মুক্তি পাওয়া খুবই প্রয়োজন।’
হেসে আমীর-উল বললেন, ‘টাকা লাগবে না, রণেশ আমার বাল্যবন্ধু, একসঙ্গে অতীতে জেল খেটেছি। ওর কেস অবশ্যই ভালোভাবে করব।’ বলেই একটি ওকালতনামাতে সই নিলেন। ডেপুটি জেলর আইনমোতাবেক প্রতিস্বাক্ষর করে আমীর-উলকে দিলেন। আসলেও তিনি একটি পয়সাও না নিয়ে খেটেখুটে রিটটি করে কয়েক মাসের মধ্যেই উচ্চ আদালতের নির্দেশে আমাকে মুক্ত করেন। ওই দিন ইন্টারভিউয়ের পর রাতে দেখি বিশাল এক ভূরিভোজের ব্যবস্থা। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার উপলক্ষে ভাবি নিজ হাতে রান্না করে এনেছিলেন বিস্তর আইটেম। ছিল সবই অত্যন্ত সুস্বাদু। মনে আছে, ইলিশ মাছের পাতুরির কথা যেন আজও জিভে লেগে আছে। ভাবি যে এত ভালো রান্না করতে জানতেন, তা আদৌ জানতাম না। আমি লিচু থেকে শুরু করে মৌসুমি নানা ফল দেখেছিলাম যা আমার ভাগ্যেও প্রচুর পরিমাণে জুটে গেল।
লেখক: রাজনীতিক, সাংবাদিকতায় একুশে পদকপ্রাপ্ত
আরও পড়ুন:ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা
ছয় দফায় ভিত রচিত হয়েছিল
ছয় দফা নিয়ে ‘কারাগারের রোজনামচা’য় বঙ্গবন্ধু
ছয় দফার সমর্থনে ৭ জুনের জনবিস্ফোরণ
খন্দকার মোশতাক মুক্তিযোদ্ধা নয় পাকিস্তানের দালাল
- ট্যাগ:
- মতামত




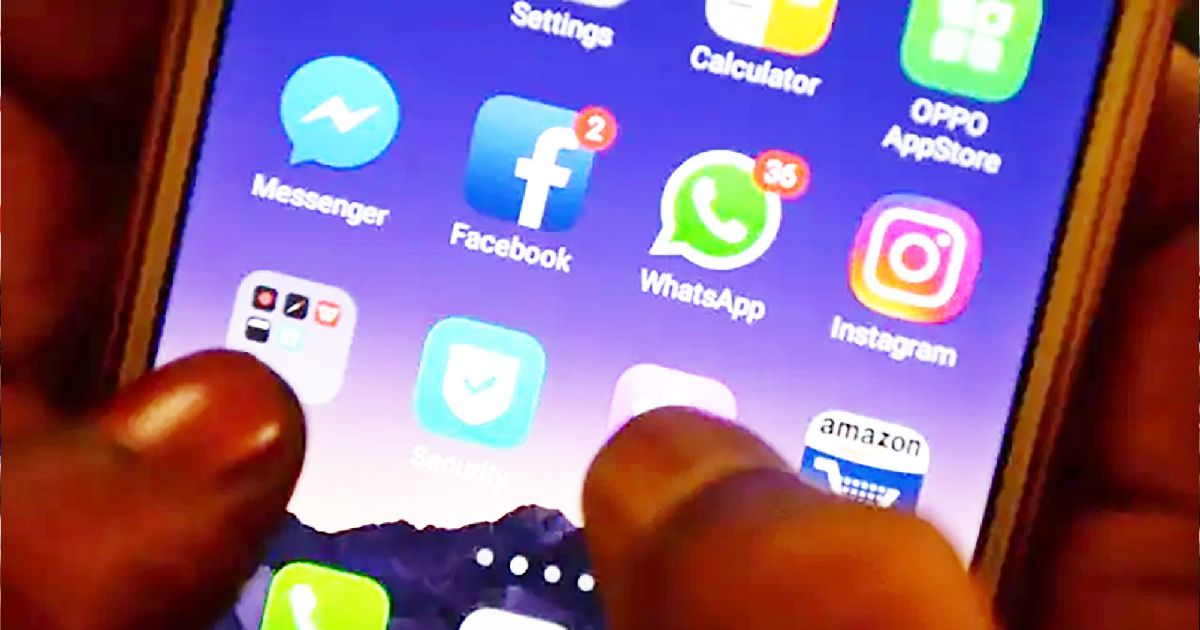







মন্তব্য