বাংলা ভাষার জন্য বাঙালি ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হওয়া প্রথম জাতি যারা পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র লাভের পর পরই আন্দোলন-সংগ্রাম এবং প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। ইতিহাসে এমন নজির এর আগে খুব একটা পাওয়া যায় না।
অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য পূর্ব বাংলার বেশিরভাগ নাগরিকই একসময় আন্দোলন-সংগ্রাম এবং ভোটদানের মাধ্যমে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি ভারত ত্যাগ করে যাওয়ার প্রাক্কালেই ধ্বনি উঠেছিল ‘নতুন পাকিস্তানের রাষ্ট্রের ভাষা হবে উর্দু’।
পূর্ব বাংলার ভাষা সচেতন মহল এর প্রতিবাদ করে লেখালেখি করেন, বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, পূর্ব বাংলার প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে মাত্র ৩ শতাংশ মানুষ উর্দু ভাষাভাষী। সুতরাং পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর উর্দু চাপিয়ে দেয়া কোনোভাবেই নতুন রাষ্ট্রের উচিত হবে না। কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠী কিছুতেই এই যুক্তি মানতে চায়নি। ফলে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে দাবি উচ্চারিত হতে থাকে, উর্দুর বিরোধিতা করা হতে থাকে।
মুসলিম যুবলীগ, তমদ্দুন মজলিশসহ বুদ্ধিভিত্তিক রাজনৈতিক সচেতন সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত সৃষ্টি শুরু করে, গড়ে তোলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নামক সাংগঠনিক কমিটি। অথচ সবেমাত্র জন্ম নেওয়া এই রাষ্ট্রটির প্রতি মানুষের আবেগ, উচ্ছ্বাস, বিশ্বাস ও নানা স্বপ্নের জাল তখন সবেমাত্র বিস্তার লাভ করার সময়। কিন্তু সেই সময়ই পূর্ব বাংলার ভাষা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান সরকারের আঘাত যেন সবাইকে হতভম্ব করে দেয়। এখান থেকেই শুরু হয় মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করার এক আন্দোলন যা ক্রমেই ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে পূর্ব বাংলার জাতীয় জীবনে পরবর্তী বছরগুলোতে দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে।
১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল ও জনক বলে খ্যাত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবেই ঘোষণা করলেন, ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা’। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ ও প্রতিহত করার ঘোষণা এলো তরুণ ছাত্রসমাজ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে। কেননা ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর পরবর্তী সময় থেকেই মাতৃভাষা বাংলা-কেন্দ্রিক একটি শিক্ষা-সাংস্কৃতিক আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির ৪ তারিখ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়। এই সংগঠন শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুসলিম লীগ সরকারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করতে থাকে।
শেখ মুজিবুর রহমান এই সংগঠনের শুধু প্রতিষ্ঠাতাই নন, ভাষা আন্দোলনেরও অন্যতম একজন সংগঠক এবং উদ্যোক্তা। মার্চ মাসে তিনি এবং আরও কয়েকজন নেতা একটি লিফলেট শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেন। এতে মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে আন্দোলন ও সংগ্রামের কথা দাবি আকারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ১১ মার্চ সচিবালয়ের কাছে মিছিল সহকারে বাংলা ভাষার দাবিতে অগ্রসর হলে মুজিবসহ কয়েকজন গ্রেফতার হন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জোড়দার হয়। সেই সময় মুসলিম লীগ সরকার এইসব আন্দোলনকে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করে। এরপর জিন্নার ২৩ মার্চ রেসকোর্স ময়দান ও ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর ঘোষণা শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদমুখর করে তোলে। ভাষা আন্দোলনের এই সময়টিকে প্রথম পর্ব হিসেবেও অভিহিত করা হয়।
এরপর পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৪৯ সালে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবি জানালে শাসকগোষ্ঠী তা মেনে নেয়নি। ওই বছরই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা লাভের পর বাঙালির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক দাবির আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এভাবেই পূর্ব বাংলায় মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষার আন্দোলনের পক্ষে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষা সাংস্কৃতিক মোর্চা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে- যা ১৯৫২ সালে আবার যখন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের মুখে উর্দুর পক্ষে ঘোষণা আসে, তখন ঢাকা শহরে সর্বত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আন্দোলনে মুখরিত হয়ে ওঠে।
ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকেই ছাত্র আন্দোলন মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষায় দীপ্তকণ্ঠে এগিয়ে চলতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের এই পর্বে রাজনীতিবিদগণ ছাত্রনেতৃত্বকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে আন্দোলনকে বেগবান করতে সহযোগিতা করেন। আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী তখন বাইরে এবং যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিব জেলের অভ্যন্তরে থেকে ছাত্রদের আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ডাকা ছাত্র ধর্মঘট সফল করার প্রস্তুতিও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে থাকে।
এই প্রেক্ষাপটে ২০ তারিখ সরকারের পক্ষ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি মিছিল সমাবেশে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সেই মিছিল ২১ তারিখ থামানো যায়নি। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ব্যানার-সমেত স্লোগান সহকারে ছাত্ররা যখন মিছিল নিয়ে অগ্রসর হয়, তখন একদিকে গুলি অন্যদিকে মিছিলে অংশগ্রহকারীদের গ্রেপ্তার চলছিল অব্যাহতভাবে। এতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন সালাম, বরকত, রফিক, শফিউলসহ বেশ কয়েকজন। অনেকে আহত হলেন আবার অনেকে জেলে গেলেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম ছাত্র-জনতার মিছিলে এমন বেপরোয়া গুলি, নির্বিচারে হত্যা ও গ্রেপ্তারের ঘটনায় পূর্ব বাংলা ফেটে পড়ল। পরদিন ঢাকায় হরতাল পালিত হলো। সারা দেশে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল।
ঘটনার আকস্মিকতায় পূর্ব বাংলার জনগণ হতবাক হয়ে পড়ে। তারা কোনোদিন ভাবতে পারেনি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র লাভের পর মাতৃভাষার ওপর শাসকগোষ্ঠী ক্রমাগতভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকবে বছরের পর বছর ধরে, বাঙালির শত আবেদন নিবেদন উপেক্ষা করবে এবং ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি ছুড়ে প্রাণসংহার করবে।
বাস্তবে ঘটেছিল পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে এক অবিশ্বাস্য রাষ্ট্রের তাণ্ডব যা ছিল মূলতই বাঙালির হাজার বছরের মাতৃভাষা বাংলাকে কেড়ে নেয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানিকরণের এক অশুভ ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র পাকিস্তান অব্যাহতভাবে পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে চালিয়েছিল। তবে এর বিরুদ্ধে ক্রমেই শিক্ষাঙ্গন থেকে সাধারণ মানুষও স্বোচ্চার হতে থাকে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা-কেন্দ্রিক আন্দোলন পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবোধে ফিরে আসার এক আন্দোলন ও সংগ্রামের উপলব্ধি হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকে।
১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের ভরাডুবি ঘটে। এরপর পাকিস্তানের সরকার ষড়যন্ত্রের নতুন নতুন গুটি চালতে থাকে। ভেঙে দেয়া হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার, বসানো হয় তাঁবেদার মুসলিম লীগের জোড়াতালি দেয়া সরকার, পূর্ব পাকিস্তান ততদিনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটার এক নতুন প্লাটফর্মে। ফলে পাকিস্তানের বাংলা ও বাঙালি বিরোধী ষড়যন্ত্র মসৃণভাবে চলতে পারেনি, বরং পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি সরকারকে মেনে নিতে হয়, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে এর অর্ন্তভুক্তিও ঘটে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে একটি সাম্প্রদায়িক, সামরিক, অগণতান্ত্রিক চরিত্রকে ধারণ করে টিকে থাকার চেষ্টা করে। এর ফলে পূর্ব বাংলার রাজনীতি ক্রমেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। সেটিকেও পাকিস্তান সরকার স্তব্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ১৯৬২ সালে ছাত্র-আন্দোলন এবং ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের ৬ দফা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালে সকল বাধা অপসারণ করে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।
এই অভ্যুত্থান পূর্ব বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক উত্থান পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেও পাকিস্তানের আগের ষড়যন্ত্রকে পূর্ব বাংলায় টেকাতে পারেনি। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ নিরঙ্কুশ সমর্থন জানায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি। পশ্চিম পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে তখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলা ও বাংলাদেশ-কেন্দ্রিক চেতনার মহাসমাবেশ ঘটে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষা ও জাতীয়তাবাদের নতুন আবহকে উপলব্ধি করতে পারেনি। তারা ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। পূর্ব বাংলাকে তারা অস্ত্রের মাধ্যমে পদানত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ততদিনে সেটি দেরি হয়ে গিয়েছিল।
শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে নির্বাচিত সরকার গঠনের কথা ছিল, তা উপেক্ষিত হওয়ার পরিণতি হলো স্বাধীনতার এক দফা। ৭ মার্চ তারিখে সেই ঘোষণাই উচ্চারিত হয়েছিল। তারপরও পাকিস্তান বুঝতে পারেনি এই ঘোষণার প্রতিধ্বনি কত শক্তিশালী হতে পারে। তারা ট্যাংক, কামান দিয়ে ২৫ মার্চ রাতে বাঙালির কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়া হলো বিপরীত। ২৬ মার্চ থেকে স্বাধীনতার জন্য বাঙালি প্রথমে প্রতিরোধ, এরপর এক বিশাল মুক্তিযুদ্ধ ও জনযুদ্ধ সংগঠিত করে পাকিস্তানের শক্তিশালী সরকারকেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করল।
বাংলাদেশ নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। এটি ছিল ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় সূচিত ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক পথ পরিক্রমার চূড়ান্ত ফলাফল।
উল্লেখিত ভাষা আন্দোলন বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষার আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি স্বায়ত্বশাসন থেকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। তবে আন্দোলনটি একেবারেই নির্ভেজাল ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের শক্ত ভিত্তি দাঁড় করাতে পারেনি। এর কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণ ছিল।
প্রথমত, দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে বাংলা ভাষার বিকাশ ও চেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতিক ও রাজনীতিতে ব্যাপক কোনো গণভিত্তি তৈরি করতে পারেনি। কারণ ঔপনিবেশিক শক্তির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার মতো বাঙালি চেতনাকে দৃঢ়তর হতে দেয়া হয়নি। একধরনের সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করেছিল। সেক্ষেত্রে অগ্রসর হিন্দু এবং মুসলিম সমাজও সেই বিভাজনে নিজস্ব শ্রেণিস্বার্থ রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।
জাতীয় কংগ্রেস ভারতের সকল জাতিগোষ্ঠীর ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধকে রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ করতে পারেনি। এটি জোড়াতালি দিয়ে সবশ্রেণি পেশার প্লাটফর্ম হতে চেয়েছিল।
অন্যদিকে মুসলিম লীগ বৃহৎ ধনী ও অভিজাত মুসলিম পরিবারের নেতৃত্বাধীন সংগঠন হলেও সুকৌশলে ১৯৪০ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের এক উদ্ভট ধারণায় গোটা ভারতবর্ষের রাজনীতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়। এক্ষেত্রে কংগ্রেস মুসলিম লীগ ফেডারেল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা থেকে অনেকটাই নিজ ধর্ম সম্প্রদায়ের নামে বিভক্ত ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পেতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। পাকিস্তান এক্ষেত্রে অনেক বেশি সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত ফেডারেল পদ্ধতির রাষ্ট্র নিয়ে আলাদা হয়ে যায়।
পাকিস্তান উগ্র সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়ে পূর্ব বাংলাকে একটি আধা উপনিবেশিক ভূখণ্ড হিসেবে পেতে চেয়েছিল। সে কারণেই উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল। এর পক্ষে এবং বিপক্ষে নানা বিভ্রান্তি এই অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সম্প্রদায়গতভাবে বিদ্যমান ছিল। কেননা ব্রিটিশ আন্দোলনের শেষ প্রান্তে এসে স্বাধীনতার আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিভাজন ও প্রতিহিংসার যে বীজ বপন করেছিল, সেটি পূর্ব বাংলার ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলনেও সুস্থধারার বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটাতে পারেনি। কেবলমাত্র পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বৃহত্তর মানুষ ১৯৬৯ সালে এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু এর মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক উপাদান শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করার যথেষ্ট সময় পায়নি। সে কারণেই উর্দুর প্রতি সাম্প্রদায়িক দুর্বলতা, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলো এবং সমাজের একটি অংশের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। এরা পাকিস্তানকে কোনোভাবেই সমালোচনা করতে চায়নি।
১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের প্রায় ২৫ শতাংশ তাদেরই ছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও একটি অংশ সরাসরি বিরোধিতা করেছিল। এর কারণ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা- যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালে এতবড় মুক্তিযুদ্ধের বিজয় লাভের পরও মুছে যায়নি।
১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার বাংলা ভাষার বিস্তার এবং প্রয়োগের মাধ্যমে যে জাতিরাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সেটি যদি কাম্য সময় পেত তাহলে এর একটি রূপ আমরা লাভ করতে পারতাম। কারণ ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ, মাতৃভাষায় শিক্ষার বিস্তার ছাড়া কোনোভাবেই আধুনিকতার ধারণাকে লাভ করতে পারে না। সে কারণে বাংলা ভাষার চর্চা স্বাধীনতাত্তোর সেটি যদি জাপান থেকে ইউরোপ পর্যন্ত আধুনিক জাতিরাষ্ট্রসমূহের মতো শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে চর্চার সময় ও সুযোগ পেত তাহলেই কেবল এর একটি সফল পরিণতি আমরা লাভ করতে পারতাম! কিন্তু বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালের পর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আদর্শগতভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও বিকৃত জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শে ফিরে যায়।
এর ফলে বাঙালি চিরায়ত জাতিসত্তা এবং ভাষার সচেতনতা এই সময় থেকে বিকৃত ধারায় বিভ্রান্ত হতে থাকে। সাধারণ মানুষ বাঙালি ও বাংলাদেশি আত্মপরিচয়ের বিভ্রান্তিতে পড়ে, বাংলা ভাষা ও একই সঙ্গে হিন্দুত্ব ও মুসলমানিত্বের বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়া হয়। এর ফলে জাতিসত্তা ও মাতৃভাষার পরিচয়, আবেগ, চেতনাবোধ ধারণ করার স্বাভাবিকতা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি করে। আবার ফিরে আসে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত পরিচয়ের প্রাধান্যতা- যা বাঙালি জাতির মধ্যে সবকিছু নিয়ে বিরোধ ও বিভ্রান্তির বিস্তার ঘটায়।
বাংলা ভাষার প্রতি বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী যতটা জাতীয়তার ঐতিহাসিক পরিচয় থেকে নিবিষ্ট হওয়ার কথা ছিল, তাতে একধরনের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ ছড়ানো হলো। বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের মূল্য ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার পরিচয়ে ক্রমেই গৃহীত বা পরিত্যাজ্য হতে থাকে। সাহিত্যের মান ও উৎকর্ষ বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এই জায়গায় বাঙালি মুসলমানের কাছে আরবি, উর্দু ও ফার্সি শব্দের আবেদন অনেক বেশি পুণ্যতার নিরিখে সমাদৃত হতে থাকে। অথচ বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা এই সময়ে রাশ ফেলেও বৃহত্তর বাঙালি মুসলমান বাংলা ভাষার মধ্যে ধর্মীয় পরিচয়ের সন্ধান খুঁজতে থাকে। এর ফলে বাংলা ভাষার চর্চায় আমাদের মধ্যে নানা ধরনের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস জায়গা করে নেয়া শুরু করে। অন্যদিকে আরবি, ফার্সি, উর্দু শব্দের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়।
এমন পরিস্থিতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা আমাদের মধ্যে দুর্বল হতে থাকে। একইসঙ্গে বাংলা ভাষার চর্চা ও জীবন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠার বোধ ক্রমেই দুর্বল হয়ে যায়। আশি এবং নব্বইয়ের দশকে দেশীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান নতুনভাবে রাষ্ট্রের সর্বত্র সমর্থন পেতে থাকে। তবে এই সময়ে সাংস্কৃতিকভাবে উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজির আগ্রাসনও ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কর্মরত বাঙালিদের মাধ্যমে যে আর্থিক জোগান গ্রামীণসমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রবাহ সৃষ্টি করে তাতে জাতীয়তাবোধের ধারণার চাইতে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত পরিচয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি স্থান পেতে থাকে। এর ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে শুধু জাতিসত্তার বোধই বিভাজিত হয়নি, মাতৃভাষার গুরুত্বও উপলব্ধিতে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠার সমর্থন পায়নি। একুশ শতকের শুরুতে আমাদের ধনিকশ্রেণি অনেক বেশি পাশ্চাত্যের ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাদের সন্তানদের ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ইংরেজি ভাষাভাষী দেশে উচ্চশিক্ষায় পাঠিয়ে দেয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। এটি ক্রমেই মধ্যবিত্তকেও স্পর্শ করতে থাকে।
অন্যদিকে ইন্টারনেট, অনলাইন তথা তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে নতুন প্রজন্ম হিন্দি সংস্কৃতির আগ্রাসনই শুধু নয়, ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শিত নানা ধরনের মুভির নামে বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার প্রবণতাও বেড়ে গেছে। যারা এসব প্রযুক্তির অপব্যবহারের শিকার হচ্ছে তারা মাতৃভাষায় রচিত মূল্যবান গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করে না। ফলে একধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ, আপন জাতিসত্তা ও মাতৃভাষার প্রতি সৃষ্টি হয়েছে।
এটি মোটেও আমাদের নতুন প্রজন্মের মেধা, মনন, দেশপ্রেম, জাতিসত্তার আত্মপরিচয়ের সন্ধান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করার পক্ষে সহায়ক নয়। তবে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মানের যে সংকট চলছে, তাতেও বড় অংশের শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাষার জ্ঞানও প্রয়োগগত দক্ষতায় প্রয়োজনীয় মানে তৈরি হচ্ছে না। এদের মধ্যে বাংলা বা ইংরেজি কোনো ভাষাই দক্ষতার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আবার ঘরে ঘরে হিন্দি সিরিয়ালের আকন্ঠ নিমজ্জিত শিশুরা মাতৃভাষা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের চাইতে হিন্দি ও উর্দুতে কথা বলার পারদর্শিতা অর্জন করছে- যা তাদের পঠন পাঠন বা কর্মজীবনে তেমন কোনো প্রভাব ফেলছে না।
আসলে বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় ভেতর থেকে যেসব জাতিরাষ্ট্র নিজস্ব মাতৃভাষায় সমগ্র শিক্ষাকে ঢেলে সাজাচ্ছে এবং রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে তারাই কেবল জাতীয়তাবোধ ও মাতৃভাষার উন্নয়ন ঘটাতে পারছে। একমাত্র মাতৃভাষাতেই যেকোনো জাতি নিজের গভীরতম চিন্তার প্রকাশ সুন্দরতমভাবে ঘটাতে পারে। ভাষার হেজিমনি দিয়ে কোনো জাতি নিজের ভবিষ্যৎকে প্রশস্ত করতে পারবে না। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে মাতৃভাষায় সর্বস্তরে শিক্ষা-গবেষণা, প্রশাসন-বিচারসহ সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস অব্যাহত রাখা। তাহলেই জাতিসত্তা এবং মাতৃভাষার মর্যাদা সুরক্ষিত হতে পারে।
লেখক : অধ্যাপক, গবেষক

 মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী
মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী


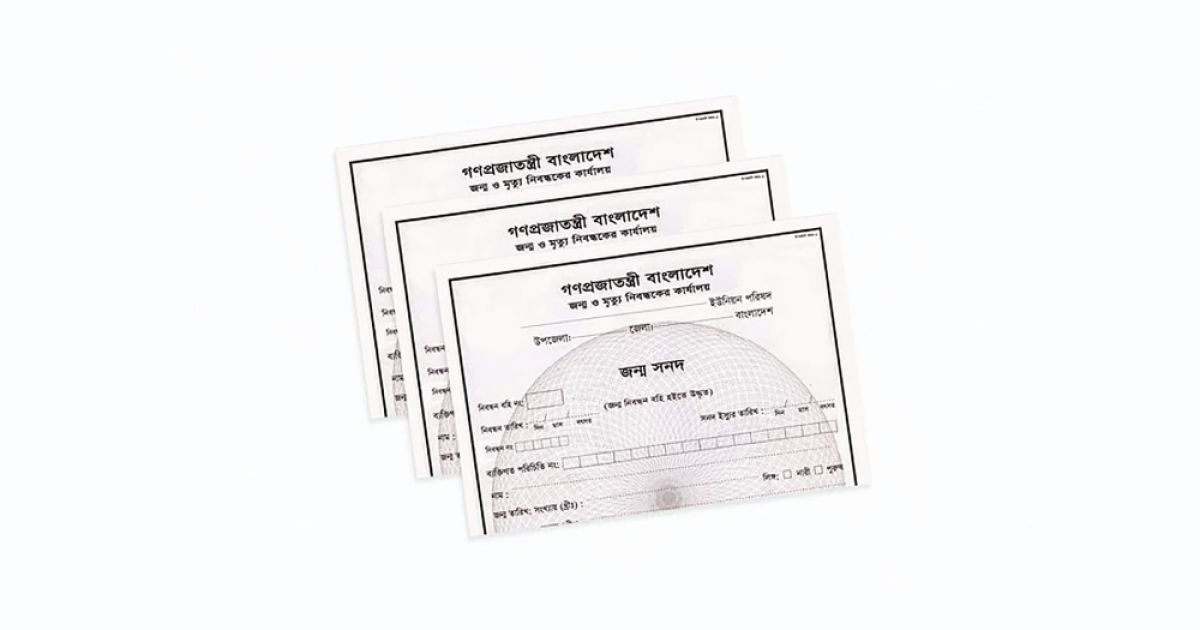






মন্তব্য